আনু মুহাম্মদ
ভূমিকা- ১
বিশ্বের অন্য অনেক অঞ্চলের মতো দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও রাজনীতিতে ধর্ম এখন আগের যে কোনো সময়ের চাইতে বেশি উপস্থিত। ধর্ম সামনে রেখে সহিংসতা, অসহিষ্ণুতা, সন্ত্রাসও বাড়ছে ক্রমেই। পাকিস্তান প্রথম থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র। তবুও সেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে সহিংস সংঘাত কখনো কমেনি বরং বেড়েছে। ইসলামের নামে বিভিন্ন মসজিদে হামলা ও মুসল্লী হত্যাও প্রায় নিয়মিত। যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পাকিস্তান এখন সন্ত্রাসের ও ড্রোন হামলার স্থায়ী ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই অঞ্চলের সবচাইতে বড় রাষ্ট্র ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ হলেও সেখানে গত কয় দশকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রসার ঘটেছে অনেক। কয়েকদফা জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে প্রায় একচেটিযা বিজয় নিয়ে সেখানে হিন্দুত্ববাদী দল ক্ষমতাসীন।
তিনদফা প্রধানমন্ত্রী হযেছেন গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত এবং ভারতে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টির নায়ক নরেন্দ্র মোদী। জোর করে ইতিহাস পরিবর্তন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ এবং বিদ্বেষও নানাভাবে বাড়ছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। নেপালে নতুন প্রণীত সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতা বিধান রেখে পাশ হলেও নেপালকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণার জন্য সেখানে আন্দোলন দাঁড় করানোর চেষ্টা এখনও বলবত আছে। নেপালের রাজনীতিতে ভারতের বর্তমান সরকার নানাভাবে হস্তক্ষেপ করছে। সামনে সেখানেও হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি প্রসারের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের সংবিধানে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ আছে, তবে সাথে আছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামও। ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ দল/জোট ক্ষমতায় ছিল দেড় দশকেরও বেশি কিন্তু এসময়েই রাজনীতি ও সমাজে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতা কমেনি বরং বেড়েছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিভিন্ন গোষ্ঠী অনেকক্ষেত্রে এই ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ দলকেও পরিচালনা করেছে। বিশ্বজুড়ে ধর্মকে ধরে সন্ত্রাস, সংঘাত ও অনিশ্চয়তা বাড়ছে। তার থেকে বেশি বাড়ছে আতংক ও এই বিষয় নিয়ে ধোঁয়াশা।
সারাবিশ্বে সংবাদমাধ্যমে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ‘ইসলামপন্থী রাজনীতির সন্ত্রাস’ নিয়ে প্রবল মনোযোগ এবং হুলস্থুল দেখা গেলেও এর উৎস সন্ধানে অনাগ্রহও দেখা যায় সেরকমই। যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত তথাকথিত ‘সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ মডেল’ জোরকদমে এগিয়ে যাবার সাথে সাথে বেড়েছে সন্ত্রাসী ভুতুড়ে গোষ্ঠী, ডিজিটাল প্রচারণা আর অদৃশ্য সরকারের তৎপরতা। দেশে দেশে পুঁজিপন্থী সংস্কার চলছে আর তার যাত্রাপথ মসৃণ করে বিভিন্ন ধর্মের নামে উন্মাদনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ‘মৌলবাদ’, ‘আধুনিকতা’, ‘পশ্চিম’, ‘ধর্ম’, ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ ইত্যাদি নিয়ে সাদাকালো বিভাজনকে প্রশ্নের মধ্যে আনার তাগিদ তৈরি হয়েছে।
এই পরিপ্রেক্ষিতে বৈশ্বিক ফ্যাসিবাদী কাঠামো বিবেচনায় রেখে বর্তমান প্রবন্ধে এসব বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। একইসাথে রাষ্ট্র, ধর্মপন্থী ও তথাকথিত সেকুলার রাজনীতির পারস্পরিক ঐক্য-বিবাদের নানা গ্রন্থি তুলে ধরে বাংলাদেশসহ বিশ্বের নানা প্রান্তের সর্বজনের বিপদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।
বিষয়ের জটিলতা
বর্তমান সময়ে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিযে আলোচনার গুরুত্ব বহুবিধ। কারণ-
প্রথমত, বিশ্বজুড়ে সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ‘ধর্মীয়’ এজেন্ডার চাপ আগের চাইতে অনেক বেশি। একই সময়ে সাম্প্রদায়িক, জাতিবিদ্বেষী, বর্ণবাদী, যৌনবাদী, অসহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়গুলোও আগের তুলনায় বেশি উপস্থিত।
দ্বিতীয়ত, ধর্মকে ভিত্তি করে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য নানা গোষ্ঠীর তৎপরতা বাড়ছে। ‘সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের’ নামে দেশে দেশে সামরিকীকরণও বাড়ছে।
তৃতীয়ত, শোষণ ও অবিচারের সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং এর থেকে মুক্তির দিশাহীনতার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের নানাবিধ সংগঠন ও তৎপরতা অনেক বেশি পরিসর তৈরি করেছে।
চতুর্থত, ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ হিসেবে পরিচিত অনেক রাজনৈতিক দলও নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে, ক্ষমতা ও ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে ধর্ম ও ধর্মীয় বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ করছে। এবং
পঞ্চমত, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা তার প্রাসঙ্গিকতা টিকিয়ে রাখতে নানাভাবে ‘ধর্মীয় সন্ত্রাস’ চাষ করছে।
ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমেই কয়েকটি প্রশ্নের মুখোমুখি হই। এগুলো হলো:
এক. ‘মৌলবাদী’ শব্দটি ধর্মপন্থী রাজনীতি বোঝাতে উপযুক্ত শব্দ কিনা।
দুই. এই রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে সবসময় ‘উদারনৈতিক’ ‘গণতান্ত্রিক’ রাজনৈতিক শক্তিগুলোর বিপরীত হিসেবে দেখা ঠিক কিনা।
তিন. তথাকথিত ‘মৌলবাদী’ রাজনৈতিক শক্তি কি পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধ কোনো শক্তি, ‘মৌলবাদ’ আর পুঁজিবাদী উন্নয়নের মধ্যে কি অন্তর্গত কোনো বিরোধ আছে?
চার. প্রান্তস্থ দেশগুলোতে ‘মৌলবাদ’ কি বৈশ্বিক পুঁজিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ তৈরি করেছে?
পাঁচ. ‘মৌলবাদ’ কি কেবল মুসলিম দেশ ও গ্রামীণ অঞ্চলের বিষয়? এবং
ছয়. ধর্মপন্থী রাজনীতি কি সমাজের গরীর নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে বা করতে পারে?
এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা ক্রমশ পেতে থাকবো আশা করি। তবে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ নিয়ে লেখার শুরুতে কয়েকটি বিষয়ে আমার অবস্থান পরিষ্কার করে নিতে চাই।
প্রথমত, সাধারণভাবে ধার্মিক মানুষের কাছে ধর্মের রূপ, আর ধর্মের একটি নির্দিষ্ট বয়ানের ওপর ভিত্তি করে কোনো গোষ্ঠীর রাজনৈতিক তৎপরতা এক কথা নয়।
দ্বিতীয়ত, নিজ নিজ ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মের মৌল আদর্শের প্রতি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাঁর/তাঁদের বিশ্বাস ও চর্চার অধিকার অবশ্যই রাখেন। তা অন্য কারও সঙ্গে না মিললে তাতে কেউ আপত্তি করতে পারেন না, যদি তা তাদের অসুবিধা না ঘটায়।
কিন্তু তৃতীয়ত, কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠী/ সংগঠন যখন ধর্মের মৌল আদর্শ নিজেদের মতো সংজ্ঞায়িত করে, এবং অন্যদের মত/বিশ্বাস/চর্চা অস্বীকার করে তা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করে তখন তা তৈরি করে সহিংস পরিস্থিতি। জোর করে চাপানোর এই মতাদর্শিক অবস্থানই ফ্যাসিবাদী রাজনীতির জন্ম দেয়।
চতুর্থত, ধর্মীয় চর্চায় যুক্ত আছেন, সেটাই তাদের জীবিকা এরকম ইমাম মুয়াজ্জিন মাদ্রাসা শিক্ষক প্রমুখকে কায়েমী স্বার্থবাদীদের সাথে গাটছড়ায় বাঁধা কতিপয় ক্ষমতাবান ধর্মীয় নেতার ভূমিকা থেকে ভিন্নভাবে দেখতে হবে। কারণ এই পেশাজীবীরা পেশাগত কারণে এবং জীবিকার প্রয়োজনে সাধারণত বিত্তবান ও ক্ষমতাবানদের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য থাকেন।
পঞ্চমত, মৌলবাদী আর সাম্প্রদায়িক এক কথা নয়। কারও মধ্যে এই দুটো প্রবণতা একসাথে নাও থাকতে পারে। মৌলবাদ ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জীবনচর্চা কাঠামো। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ধর্মের পরিচয়কে ভিত্তি করে তৈরি হলেও তাতে অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ থাকে প্রধান। সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি মানে অন্য সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বিদ্বিষ্ট, আক্রমণমুখি। একজন ধর্মবিশ্বাসী সাম্প্রদায়িক নাও হতে পারেন, যেমন একজন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ধর্মবিশ্বাসী বা চর্চাকারি নাও হতে পারেন। অর্থাৎ ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়কে নিয়ে বিদ্বেষী রাজনীতি এক কথা নয়। অভিজ্ঞতা বলে, সাম্প্রদায়িকতা অনেকসময় ধর্মীয় সংখ্যালঘুর জমিজমা সম্পদ দখলের আবরণ হিসেবেও ব্যবহার হয়।
ষষ্ঠত, ধর্মবিশ্বাসী মানেই মৌলবাদী নন। ধর্মবিশ্বাসী মানেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অনুসারী নন।
সপ্তমত, খ্রীষ্টান মানে খ্রীষ্টান সুপ্রিমেসিস্ট নয়, ইহুদী মানেই জায়নবাদী নয়, হিন্দু মানেই বর্ণবাদী নয়, ইসলামপন্থী মানেই সন্ত্রাসী নয়।
এবং
অষ্টমত, মৌলবাদ প্রাচ্যনির্দিষ্ট বা প্রাচীন মতবাদ যেমন শুধু নয়, বস্তুত এর শুরু পাশ্চাত্যেই, এবং এটি বর্তমানে ‘আধুনিক’ পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই ফলাফল। ইহজাগতিকতা বা সেকুলারিজম এবং গণতন্ত্রও পশ্চিম নির্দিষ্ট এবং ‘আধুনিক’ কালের বিষয় শুধু নয়। এর বহু ধারা বিভিন্নকালে মুসলিম বিশ্ব সহ প্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকায় বহুকাল আগে থেকেই পাওয়া যায়।
ঐক্য অনৈক্য- ২
মুসলিম, হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ বা ইহুদী যে ধর্মেরই হোক এর অনুসারী রাজনৈতিক শক্তি স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থ বা ‘ঐশী বিধান নিয়ে নিজ নিজ ব্যাখ্যার ওপর ভর করেই তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। বৌদ্ধ ধর্ম নিরীশ্বর হলেও তার মধ্যেও বিধি বিধান নিয়ে ব্যাখ্যা ও ভূমিকার তারতম্য হয়। বিভিন্ন ধর্মের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তি ইহজগতের রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ, আইনকানুন, প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রেও ধর্মগ্রন্থের নিজ নিজ ব্যাখ্যাকে বিতর্কের উর্ধ্বে রাখতে রায় দেন। এগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলাও অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে একটি বাড়তি বিষয় হলো বর্ণপ্রথা, যা এর মৌলভিত্তি।

মৌলবাদী বা ফান্ডমেন্টালিস্ট শব্দটি এসেছে মার্কিন প্রটেস্টান্ট খ্রীষ্টানদের মধ্য থেকে। তাঁরা তুলনামূলকভাবে উদারনৈতিক খ্রীষ্টানদের থেকে নিজেদের পার্থক্য বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করতেন। এখন এই শব্দটি ইসলামপন্থী রাজনীতি প্রসঙ্গেও ব্যবহৃত হয়। মৌলবাদী বলতে সাধারণভাবে বোঝানো হয়, ধর্মগ্রন্থ যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিধিবিধান জারি করেছে তার মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান খোঁজা, এবং এর বাইরে কোন কিছু গ্রহণ করতে অসম্মতি। এর অর্থ হলো সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন তাদের বিবেচনাযোগ্য নয়। সেই হিসেবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথেও তাদের মিলবার কথা নয়। এই জন্য এদেরকে অনেকসময় ‘প্রাক পুঁজিবাদী’ শক্তিও বলা হয়।
কিন্তু বিশ্ব জুড়ে বহু ধর্মপন্থী দলের কার্যক্রম থেকে তার প্রমাণ মেলে না। ধর্মের বাণিজ্যিকীকরণ, নেতাদের জীবনযাপন, ব্যাংক বীমাসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে দক্ষ বিনিয়োগসহ অর্থনৈতিক নীতি- তৎপরতা ইত্যাদি বহু কিছুই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মান্য করেই কাজ করে। নেতাদের অনেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সুফলভোগীও বটে।
তাছাড়া বর্তমান সকল ধর্মপন্থী রাজনীতির বড় অংশই আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর। তাদের অধিকাংশ পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই একটি নির্ধারিত সংস্করণ তৈরির জন্য চেষ্টা রত, তা বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বায়নেরও সুফলভোগী। যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের সাথে সাথে ধর্মপন্থী রাজনীতির বিস্তার ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরিতেও সহযোগী হয়েছে।
পার্থক্য এখানেই যে, তাদের অনেকে এই ব্যবস্থার ওপর ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সচেষ্ট। যেমন বিজেপি আরএসএস পুঁজিবাদের কট্টর বা নয়া উদারনৈতিক ধারা অনুসরণ করছে হিন্দুত্ববাদের আবরণ দিয়ে। জামায়াতে ইসলামীর অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মসূচি অনুযাযী ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মুনাফাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক তৎপরতা তাদের সমাজ-অর্থনীতি মডেলের দুটো গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। বলা হয়, অর্থনীতির একচেটিয়াকরণ ও বৈষম্য ঠেকাতে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা থাকবে। এই ব্যবস্থা পরিচালিত হবে ‘ঐশী নির্দেশ’ বা ‘আল্লাহর আইন’ অনুযায়ী। কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক ঈশ্বরের পক্ষে তা কে নির্ধারণ করবেন? করবেন ক্ষমতাবানরা, এর বিরুদ্ধে ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ খুবই সীমিত। একদিকে শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এই দুটোর সমন্বয় প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাই নির্দেশ করে।
তবে কোনো ধর্মই ইতিহাসের বাইরে নয়, স্থান কাল নিরপেক্ষ নয়। সেজন্য সকল ধর্মের মধ্যেই স্থান ও কালের ছায়া আছে। সকল ধর্মের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন কাল ও স্থান ভেদে নানা মত ও পথের সন্ধান পাওয়া যায়। অভিন্ন গ্রন্থ বা ধর্মীয় কাঠামো থেকে এই ভিন্ন ভিন্ন মত ও তরিকা তৈরি হয় স্থান, কাল ছাড়াও সামাজিক অর্থনৈতিক মতাদর্শিক অবস্থানগত ভেদের কারণে। অর্থাৎ ধর্মের ব্যাখ্যা ব্যক্তি/গোষ্ঠী/মতাদর্শিক অবস্থান ভেদে ভিন্ন হতে পারে।
প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে তো বটেই, একই ধর্মের বিভিন্ন ধারা ও উপধারার মধ্যেও সংঘাত বিদ্বেষ তাই অনেক পুরনো। ইসলাম ধর্মের মধ্যেও এর কমতি নেই। সপ্তম শতকে আরব বিশ্বে তৎকালীন বিদ্যমান ব্যবস্থার নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইএর মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন হয়। পরবর্তী কালে এই ধর্ম ব্যাখ্যা অনুসরণে এমনকি কুরআনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, হাদিসের বিভিন্ন ভাষ্য ব্যাখ্যায় বহুধরনের মত পথ তৈরি হয়। এর মধ্যে বৈষম্যবাদী, নিপীড়নমূলক বহু মত পরীক্ষা করলে তার সাথে সেই সেই সময়ের ক্ষমতাবানদের যোগ পাওয়া যায়। আবার সাম্য ও সংবেদনশীল মতও পাওয়া যায় যার সাথে মানুষের লড়াই এর যোগ আছে।
স্পষ্টতই বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের অনুসারী উগ্রপন্থী রাজনীতির প্রধান ধারাগুলোর মধ্যে কিছু অভিন্ন উপাদান পাওয়া যায় যা আবার অনেক ক্ষেত্রে ধর্মবহির্ভুত কিছু রাজনীতির ধারা- যেমন শ্বেতাঙ্গ উগ্রপন্থী, উগ্র জাত্যাভিমানী, যৌনবাদী ইত্যাদি ধারার সঙ্গেও মেলে। । ভারতে বিজেপি-শিবসেনা-আরএসএস, যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপে খ্রীষ্টান মৌলবাদী উগ্রপন্থী শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী জাতি ও ধর্ম বিদ্বেষী থেকে শুরু করে জামায়াত-আল কায়েদা-তালেবান-আইসিস এদের সবার মধ্যেই কিছু অভিন্ন প্রবণতা কমবেশি পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে উচ্চকিত বা প্রচ্ছন্ন বক্তব্যের সাধারণ দিকগুলো নিম্নরূপ:
১. মানুষ ঐশী ক্ষমতার সৃষ্টি। ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই ঐশী গ্রন্থ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা বিশ্লেষণ ক্ষমতা বা অধিকার সকল মানুষের নাই। এই দায়িত্ব নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ধারণ করেন। এরা পূর্বনির্ধারিত ধর্মীয় নেতা।
২. এই বিশ্বাস কাঠামো এবং তাদের ইহজাগতিক জীবন অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট উচ্চক্রম অনুযায়ী কঠোর আইন দ্বারা সংগঠিত ব্যবস্থায় পরিচালিত হতে হবে।
৩. ‘ঈশ্বরের বিধান’ হিসেবে ধর্মীয় নেতাদের স্বীকৃত বিষয়গুলো নিয়ে কেনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। ‘মানুষ তৈরি’ কোনো বিধান দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপন করা যাবে না।
৪. একই ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধারা উপধারা গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য ধর্ম বা বিশ্বাসের মানুষ বিশেষ বিবেচনায় থাকবেন, সমান মর্যাদা নিয়ে নয়।
৫. নারীকে পূর্ণ মানুষ হিসাবে স্বীকারে অনীহা, ভূমিকা নির্দিষ্ট পরিসরে সীমিতকরণ। ঘরে ও বাইরে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নকে বৈধতা দানের যুক্তি; বয়ানে নারীকেই সকল ঝামেলার কারণ, পাপের আধার, বিপজ্জনক, অনিয়ন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত করা। লিঙ্গীয় বৈচিত্র অস্বীকারের প্রবণতা।
৬. গর্ভপাত, নির্ধারিত বিধি বিধানের বাইরে নারী পুরুষ সম্পর্ক পাপ হিসেবে বিবেচিত।
৭. নির্দিষ্ট কাঠামোর বাইরে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা গ্রহণযোগ্য নয়। ধর্মের কাঠামোর মধ্যে থেকেও স্বাধীন চিন্তা বা (কর্তৃত্বের সাথে) ভিন্নমত হুমকির সম্মুখীন। লেখক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, ধর্মতাত্ত্বিক অনেকেই বিভিন্ন সময়ে নির্যাতিত।
বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলন, সশস্ত্র সংগ্রাম কিংবা সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার তৎপরতা আগের তুলনায় বেড়েছে। তবে ইসলামপন্থী রাজনীতির কোন একক বা সমরূপ চেহারা নেই। কারও কাছে এর লক্ষ্য- ওপর থেকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সমাজকে পরিবর্তিত করা, কারও কাছে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে রাজনীতিকে প্রভাবিত করা। আবার ইসলামের ভিত্তি যে কুরআন তার ব্যাখ্যায় হাজারো মত। ইসলামের মুক্তিকামী ব্যাখ্যার পাশাপাশি নারীবাদী ব্যাখ্যা ইসলাম সম্পর্কে অনেক নতুন চিন্তাও যোগ করেছে ।
সমাজে ইসলাম কায়েম করা সবার কাছে রাজনীতিও নয়। উল্লেখযোগ্য কিছু ধারা আছে যারা ব্যক্তিকে ইসলামের পথে আনার মাধ্যমে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নীতি অনুসরণ করেন। সুফীবাদী ধারা ধর্মমত নির্বিশেষে মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে ঈশ্বরের সাথে প্রেম এবং সবার মধ্যে ঐক্যের আহবান নিয়ে হাজির হয়।
ইসলামী রাষ্ট্র অতীতে আমরা অনেক দেখেছি, বর্তমান বিশ্বেও তা দুর্লভ নয়। অতীতে বিভিন্ন স্থানে ও কালে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ ভিন্ন ভিন্ন দেখা গেছে। ইসলামের শুরুতে খেলাফত স্বল্পস্থায়ী ছিলো, সেখানে রাজতন্ত্র অনুমোদিত ছিলো না। হজরত ইমাম হোসেনের ঘাতক ইয়াজিদকে দিয়েই রাজতন্ত্র শুরু, যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত আছে। মধ্যপ্রাচ্যে সৌদী আরব, কাতার, কুয়েত, জর্দান, সংযুক্ত আরব আমিরাত কথিত ইসলামী শাসনব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে রাজতন্ত্র অনুমোদিত আইন বিধান ও প্রতিষ্ঠান সেখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর। ইসলাম ধর্মে অনুমোদিত না হলেও এদের রাজতন্ত্রী ব্যবস্থাই মুসলিম বিশ্বে সবচাইতে প্রভাবশালী। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতহলেও দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক, বিশেষত নারী শিক্ষা/অধিকারের প্রশ্নে বিশাল তফাৎ। ইরান ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত। এখানে ধর্মীয় নেতা ও নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং পার্লামেন্টের একটি সমন্বয় তৈরি করা হয়েছে।
সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ’ এবং শত্রু মিত্র খেলা- ৩
আমরা জানি যে, পুঁজিবাদের সম্প্রসারণে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা খুবই সহায়ক হয়েছিলো। আর উপনিবেশগুলোতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্প্রসারণে পশ্চিমা মিশনারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো, ভূমিকা ছিলো স্থানীয় এক ধরনের ধর্মীয় নেতা ও ক্ষমতাবানদেরও। আবার ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী অবস্থানেও কোনো কোনো মিশনারী ও স্থানীয় কোনো কোনো ধর্মীয় নেতার ভূমিকা দেখা গেছে।
উত্তর উপনিবেশকালে প্রান্তস্থ দেশগুলোতে খুঁটি ধরে রাখতে, বিপ্লব ঠেকাতে পুঁজিবাদী কেন্দ্র বা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো ধর্মীয় শক্তি ব্যবহারে ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে। মূলধারার চার্চ সাম্রাজ্যবাদের খুঁটি হিসেবে বরাবরই কাজ করেছে। তারা একদিকে মুসলিম রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছে অন্যদিকে ইসরাইলকে একটি বিষফোঁড়া হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে মধ্য দিয়ে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের দীর্ঘমেয়াদী অবস্থান পাকাপোক্ত করেছে। মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে তাদের অনুগত ইসলামপন্থী দল ও ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে বিপ্লব বিরোধী আতংক সৃষ্টি করবার কাজ সহজ ছিলো। বস্তুত এই ধর্মপন্থীরা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে জনগণের মুক্তির লড়াই ঠেকাতে সামরিক বেসামরিক স্বৈরশাসকদের সমর্থন দেবার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের পথই সুগম করেছে।
এভাবেই যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ৮০ দশক পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক ধর্মপন্থী সংগঠন, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে ধর্মরক্ষার নাম করে নিজেদের আধিপত্য নিশ্চিত করার কাজে ব্যবহার করেছে। এর একটি বড় উদাহরণ আফগানিস্তান। প্রথমে মুজাহেদীনদের মাধ্যমে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সমর্থিত সরকার উচ্ছেদ করে যুক্তরাষ্ট্র। সেইসময় আফগান মুজাহেদীনদের সবরকম পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে তারা- প্রশিক্ষণ দিযেছে, অস্ত্র দিয়েছে, অর্থ দিয়েছে। এর অংশীদার ছিল সৌদী আরবও। ইউএসএইড সরবরাহ করেছে ইসলামের নামে সহিংস উন্মাদনা সৃষ্টির মতো বই, শিশুদের পাঠ্যপুস্তক। যার মধ্যে সোভিয়েত সৈন্যের চোখ উপড়ে ফেললে বেহেশতে যাবার প্রতিশ্রুতিও ছিলো। আফগানিস্তানে সিআইএ-র এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠের ভূমিকা পালন করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। সামরিক শাসনের মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউল হকের মতো এক বাধ্য নিষ্ঠুর সামরিক জেনারেলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা সেসময় যুক্তরাষ্ট্রের খুব কাজে দিয়েছে।
মুজাহেদীনদের অস্থিতিশীল শাসনের সময়েই একপর্যায়ে আকস্মিকভাবে বিশাল শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয় তালিবান। মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যাদের অস্ত্র, সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ এবং কৌশলগত সমর্থন সবই যোগান দিয়েছে সেই একই যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম দফায় তালিবানরা আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখলের সূচনা করে ১৯৯৭ সালের ২৪ মে। ঠিক তার আগের দিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ ব্যবসা জগতের মুখপাত্র ওয়াল স্ট্রীট জার্ণাল আফগানিস্তান নিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সেখানে লেখা হয়:
“আফগানিস্তান হচ্ছে মধ্য এশিয়ার তেল, গ্যাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক গ্যাস রফতানির প্রধান পথ।…তাদের পছন্দ কর বা না কর ইতিহাসের এই পর্যায়ে তালিবানরাই আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সবচাইতে উপযুক্ত।” (জার্ণাল, ১৯৯৭)
দুদিন পর অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের ২৬ মে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমস লেখে:
“ক্লিনটন প্রশাসন মনে করে যে, তালিবানদের বিজয় ইরানের পাল্টা শক্তি হিসেবে দাঁড়াবে..এমন একটি বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত করবে যা এই অঞ্চলে রাশিয়া ও ইরানের প্রভাবকে দুর্বল করবে।” (টাইমস, ১৯৯৭)
মার্কিন তেল কোম্পানি ইউনোকাল, যারা ১৯৯৯ থেকে ২০০৩ সময়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে গ্যাস রপ্তানির জন্য অনেক চেষ্টা করেছে, ক্লিনটন প্রশাসন ও ওয়াল স্ট্রীট জার্ণালের অবস্থানকে ‘খুবই ইতিবাচক অগ্রগতি’ বলে অভিহিত করে। এই কোম্পানি বিশ্ববাজারে বিক্রির জন্য তুর্কমেনিস্তান থেকে আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল নেয়ার প্রকল্প নিয়ে অপেক্ষা করছিলো।
একইবছর যুক্তরাষ্ট্র সামরিক দিক থেকে আরও অনেক শক্তিশালী ও আক্রমণাত্নক প্রকল্প গ্রহণ করে, যার শিরোনাম ছিলো: “প্রজেক্ট ফর দ্য নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি”। এতে যারা স্বাক্ষর করেন তাঁদের মধ্যে ইউনোকাল কর্মকর্তা, অস্ত্র ব্যবসায়ী সহ আরও ছিলেন বৃহৎ ব্যবসা ও হোয়াইট হাউসের দীর্ঘদিনের প্রভাবশালী ব্যক্তি ডিক চেনী, ডোনাল্ড রামসফেল্ড, জেব বুশ এবং ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা প্রমুখ। বিশ্বব্যাপী ‘নয়া উদারতাবাদী’ ধারার সংস্কার, দখল, আধিপত্যের নতুন পর্ব আরও জোরদার হয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে।
যাইহোক, ১৯৯০ এর শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্ব আধিপত্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শত্রুপক্ষ দরকার হয়। ১৯৯১ সালে প্রথম দফা ইরাক আক্রমণের মধ্য দিয়ে পরবর্তী কয়েক দশকের যাত্রাপথ নির্মিত হয়। একদিকে ‘গণতন্ত্র’ ও ‘শান্তি’র প্রতিপক্ষ ‘সন্ত্রাসী’ হিসেবে সবরকম বিদ্বেষী প্রচারণা, বৈষম্য ও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতে থাকে মধ্যপ্রাচ্য, আরব ও মুসলমান পরিচয়ের মানুষেরা অন্যদিকে রাজা বাদশাসহ মুসলিম প্রধান দেশের শাসকদের দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদী এই নকশা বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনে। এই সময় থেকে ‘ইসলামী সন্ত্রাসী’র তৎপরতাও বেশি বেশি দেখা যায় যা এই নকশা এগিয়ে নিতে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।
২০০১ সালে নিউইয়র্কের ‘টুইন টাওয়ার’ হামলার পর থেকে এই কর্মসূচির অধিকতর সামরিকীকরণ ঘটে। ফুলিয়ে ফাপিয়ে তোলা স্পষ্ট অস্পষ্ট, ঘোষিত অঘোষিত, ‘সন্ত্রাসী’দের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে তথাকথিত ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ একটি বৈশ্বিক এজেন্ডার রূপ দেয়। আরব বিশ্বে রাজতন্ত্রকে ভর করেই এই সন্ত্রাসী আধিপত্য বিস্তৃত হলেও পুরনো মিত্রদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে যুক্তরাষ্ট্র, মিডিয়াসহ তাদের নানা সংস্থার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমান বিদ্বেষী প্রচারণা জোরদার হয়। এই প্রচারণার প্রতিক্রিয়ায় ধর্মীয় পরিচয় ও রাজনীতির ক্ষেত্রও উর্বর হতে থাকে। অপমান, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষোভের ওপর ভর করে বিশ্বজুড়ে ইসলামপন্থী রাজনীতির নতুনভাবে প্রসার ঘটে।
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কমপ্লেক্সের সঙ্গে ইসলামপন্থী জঙ্গী সশস্ত্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর যে যোগ তৈরি হয়, যেভাবে তার আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয় তার ধারাবাহিকতা পরেও অব্যাহত থাকে। এর বিস্তৃতি ঘটে কয়েক দশক জুড়ে। বস্তুত যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থার কাগজপত্র কখনও প্রকাশিত হলে এর অনেক অজানা তথ্য জানা যাবে। উইকিলিকস এ কিছু প্রকাশিত হয়েছে। আইসিস, তালেবান, আল কায়েদা ইত্যাদি নামে পরিচিত যেসব গোষ্ঠীকে দমন করবার কথা বলে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে দখলদারিত্বের নতুন জাল ফেলে তাদের প্রায় সবাই মার্কিনীদেরই সৃষ্ট বা লালিত পালিত।
এগুলোর সূত্রে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নারী পুরুষ শিশুসহ বহু নিরীহ মানুষ খুন হয়েছে, মসজিদ, মন্দির গীর্জা, মেলা, উৎসব, ভাস্কর্য আক্রান্ত হয়েছে। ইসলামের নাম নিয়ে এইসব গোষ্ঠীর বর্বর দিগভ্রান্ত সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তাহীনতা আরও বেড়েছে। রাষ্ট্রের দমন পীড়ন সহিংসতা বেড়েছে, বিশ্ব অশান্তি বেড়েছে। এগুলোকেই কেউ কেউ ‘জিহাদ’ কেউ কেউ ‘সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই’ বলে মহিমান্বিত করতে চান। মোহমুক্ত থাকলে এসব বয়ান যে কতো ভ্রান্ত তা উপলব্ধি কঠিন নয়। কারণ এসব আক্রমণ- সন্ত্রাস বিশ্বের ক্ষমতাবান রাষ্ট্র, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার বিরুদ্ধে দেখা যায় না। সেকারণে তাদের দুর্বলও করে না, বরং তাদের দমন পীড়নের ব্যবস্থার আরও বিস্তৃতির পক্ষে যুক্তি তুলে দেয়। সেই সূত্র ধরেই গত আড়াই দশকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিভাবকত্বে পরিচালিত ‘সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের’ নামে দেশে দেশে জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস জুলুম আরও বেড়েছে। রাষ্ট্র আরও সশস্ত্র এবং নৃশংস হয়েছে। এই কাঠামোতেই অন্য অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও নতুন নতুন নিপীড়নমূলক আইন চাপানো হয়েছে, র্যাবসহ বিভিন্ন বাহিনী গঠিত হয়েছে; গুম, ক্রসফায়ার বেড়েছে; নজরদারির আয়োজন ভয়ংকর আকার নিয়েছে। তথাকথিত ‘জঙ্গী দমন’ হয়ে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রের জুলুমকে বৈধতা দানের অস্ত্র।
অনেকে এও যুক্তি দিতে চেষ্টা করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন এই ‘সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ’ ‘ইসলামী জঙ্গী’দের বিরুদ্ধে সেকুলার শক্তির পক্ষে। এটিও আরেকটি বড় ভ্রান্তি। বস্তুত নির্বাচিত এবং সেকুলার সরকার উচ্ছেদে মার্কিনী রেকর্ড অনেক। চিলিসহ ল্যাটিন আমেরিকায় এর দৃষ্টান্ত অনেক, বিশ্বের অন্য প্রান্তেও। যেমন ৭০ ও ৮০ দশকে আফগানিস্তানে সেকুলার সরকারই ক্ষমতায় ছিলো, কিন্তু তাদের অপরাধ তারা ছিলো মার্কিন বিরোধী। অথচ এই সরকারগুলো আফগানিস্তানে ভূমি সংস্কার, নারী অধিকার, শিক্ষা ও চিকিৎসা সংস্কারে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলো। এদের উচ্ছেদ করে মার্কিন রাষ্ট্র এমন শক্তিকে একের পর এক ক্ষমতায় এনেছে যারা এগুলোর ঘোর বিরোধী।
ইরাক ও লিবিয়াতেও সেকুলার সরকারই ক্ষমতায় ছিলো। তাদের কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার সমস্যা থাকলেও জাতীয় সক্ষমতা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিশুদ্ধ পানিসহ জন অধিকারের ক্ষেত্রে সেখানে অনেক সাফল্য ছিলো। যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনে সাদ্দাম ও গাদ্দাফীর শাসনব্যবস্থা উচ্ছেদের পর সেসব ব্যবস্থা তছনছ হয়ে গেছে। আর সেখানে বিভিন্ন ধর্মপন্থী গোষ্ঠীর প্রভাব, সংঘাত বেড়েছে। সর্বশেষ সিরিয়াতেও তাই ঘটলো।
এরকমও কেউ কেউ বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এসব দেশে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। শতভাগ ভুল কথা। স্বৈরাচার তাদের জন্য কখনোই সমস্যা না, বরং বিশ্বে স্বৈরাচারী শাসকদের প্রধান অংশ তাদেরই তৈরি কিংবা তাদেরই লোক। স্বৈরশাসক তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তারা বিরক্ত হয়।
কে কাকে শক্তি যোগায়- ৪
সমৃদ্ধি ও বঞ্চনার পাহাড়-৫
সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের পর গত প্রায় ৫৪ বছরে বাংলাদেশের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রথাগত বিচারে ‘অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি’র অনেকগুলো দিকই চিহ্নিত করা যায়। যেমন অবকাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে, সড়ক পথের বিস্তার ঘটেছে অনেক, পরিবহণ ও যোগাযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে, বহুতল ভবন বেড়েছে, আমদানি রপ্তানি দুটোই বেড়েছে, রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে গার্মেন্টস বড় সাফল্য তৈরি করেছে, প্রবাসী আয় বৈদেশিক মুদ্রার বিশাল মজুত তৈরি করেছে, প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক তৎপরতায় ক্ষুদ্রঋণ ও এনজিও মডেল অনেক বিস্তৃত হয়েছে, নগরায়ন বেড়েছে, মোবাইল ইন্টারনেট- শহর গ্রামে যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণে পেশাগত ও অর্থনৈতিক নতুন নতুন সুযোগ বেড়েছে, জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে অনেক বেশি যদিও মানুষের যথেষ্ট এবং নিরাপদ খাদ্যের সংস্থান হয়নি। অধিকতর নিরাপদ জীবনের জন্য মানুষের সচলতা বেড়েছে।
এই সমৃদ্ধির গতি ও ধরনের কারণে প্রত্যক্ষ সুফলভোগী হয়েছে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী। এর সামাজিক ও পরিবেশগত খেসারতও অনেক বেশি। নদীনালা খালবিল বন শিকার হয়েছে দখল ও বিপর্যয়ের । বৈষম্য বেড়েছে। এই সময়কালেই দেশে একটি অতি-ধনিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে। ‘কালো টাকা’ নামে পরিচিত চোরাই টাকার মালিকদের বিত্ত এবং দাপট বেড়েছে বহুগুণ। ঢাকা শহরে এখন একইসঙ্গে বিত্তের জৌলুস এবং দারিদ্রের নারকীয়তা দুটোই পাশাপাশি অবস্থান করে। চোরাই কোটি-কোটিপতির সংখ্যা যখন বেড়েছে তখন মাথাগণনায় দারিদ্রের প্রচলিত সংজ্ঞা বা কোনভাবে টিকে থাকার আয়সীমার নীচে মানুষের সংখ্যা চার কোটির বেশি। যদি দারিদ্র সীমায় শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, মানবিক মর্যাদার প্রশ্ন যুক্ত করা হয় তাহলে দেখা যাবে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষই অমানবিক জীবনে আটকে আছেন।
রাষ্ট্রীয় বৈরী নীতিমালার কারণেই সর্বজন বা পাবলিক সকল প্রতিষ্ঠানই একে একে ক্ষতবিক্ষত। পাশাপাশি বেসরকারি ক্লিনিক ল্যাবরেটরী ও হাসপাতাল, বেসরকারি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও, কনসালটেন্সী ফার্ম ইত্যাদিরও বিস্তার ঘটেছে অনেক। অনলাইন অফলাইন বেচা কেনা বেড়েছে, কম্পিউটর, মোবাইল, ইন্টারনেট, টিভি ইত্যাদি কেন্দ্রিক ব্যবসারও প্রসার ঘটেছে যার অনেকগুলোই আমদানিকৃত পণ্যের উপরই নির্ভরশীল। প্রচলিত উন্নয়ন ধারার কারণেই দেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিকাশ ঘটেছে বেশি। স্বনিয়োগভিত্তিক কাজের অনুপাত বেড়েছে। এছাড়া রিকশা, অটোরিকশা, বাস ট্রাক, টেম্পোসহ বিভিন্ন পরিবহণ, হোটেল রেস্তোরাঁ, ছোট বড় দোকান ইত্যাদি বেশিরভাগ মানুষের অস্থায়ী নিয়োজনের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ‘টুকটাক অর্থনীতি’ হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রমজীবী মানুষের প্রধান কর্মক্ষেত্র। এসব খাতে বেশিরভাগ কাজ অস্থায়ী, অনিয়মিত ও মজুরী নিম্নমাত্রার।
বর্তমানে বাংলাদেশে যতসংখ্যক মানুষ বিভিন্ন ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত তার চাইতে বেশিসংখ্যক মানুষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশে কর্মরত। এদের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। দেশে তাদের কর্মসংস্থান নেই। বিদেশেও তাঁদের জীবন ও জীবিকা চরম নিরাপত্তাহীনতার শিকার। অন্যদিকে এদেরই পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা অর্থাৎ রেমিট্যান্স এখন বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। দেশে সার্ভিস সেক্টরের দ্রুত বিকাশ হলেও তা কর্মসংস্থানকে খুবই অস্থায়ী, নাজুক ও নিম্ন আয়ের ফাঁদে আটকে রেখেছে।
সামরিক শাসন ও জামায়াতের প্রত্যাবর্তন – ৬
যুদ্ধাপরাধীর বিচার ও হেফাজতের আবির্ভাব- ৭
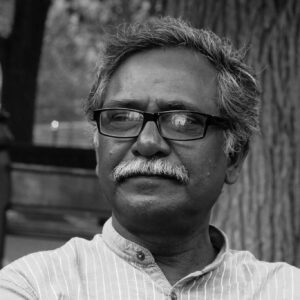
লেখক, গণবুদ্ধিজীবী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক, ‘সর্বজন কথা’ পত্রিকার সম্পাদক।


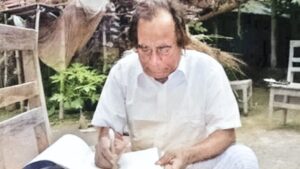

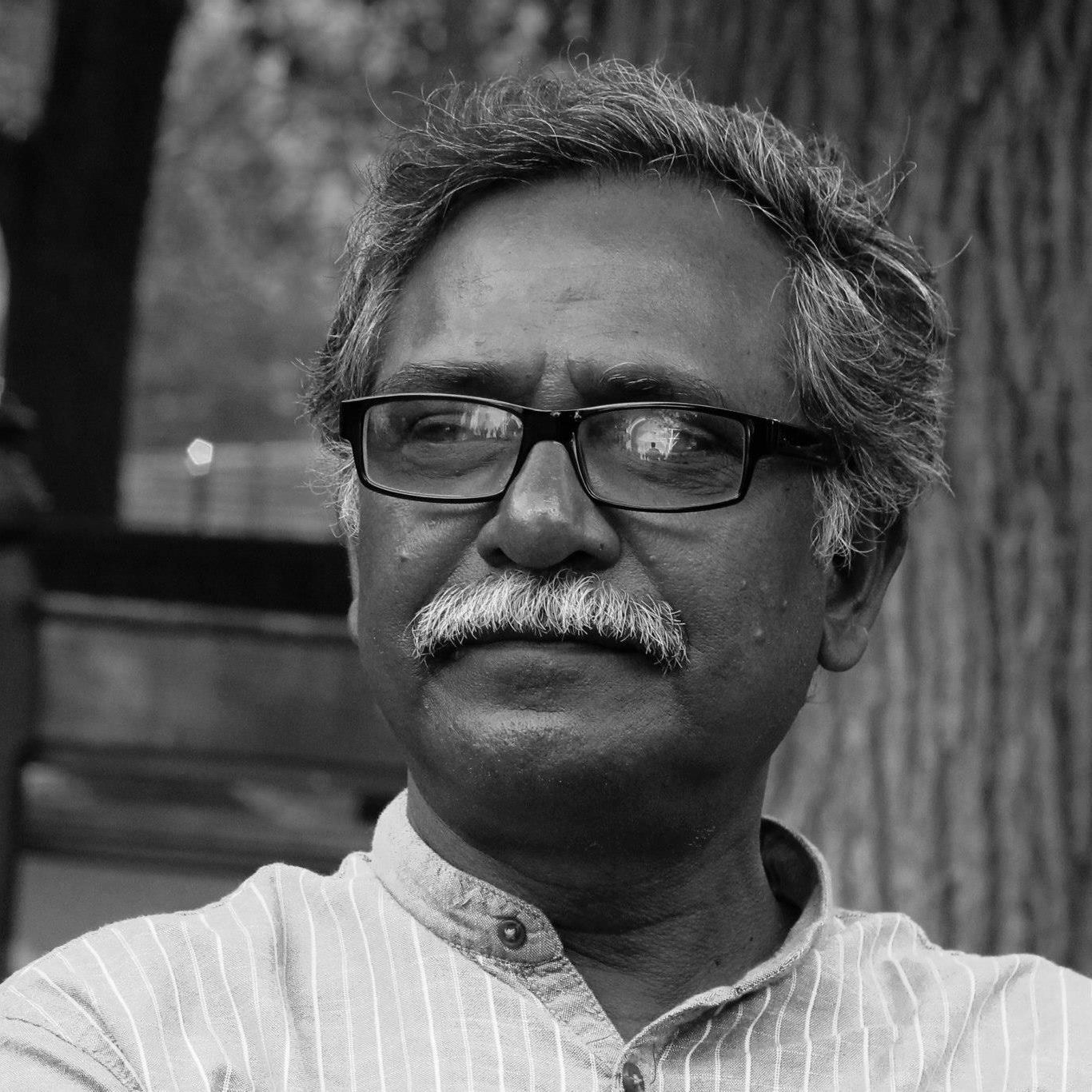
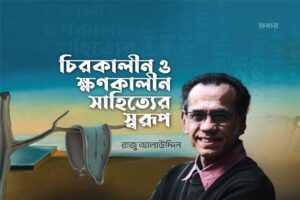
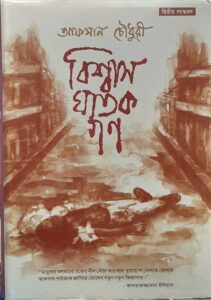
Leave a Reply