সৈয়দ তারিক
প্রায় সব ধর্মের রয়েছে একটি আনুশাসনিক ও শাস্ত্রীয় দিক এবং একটি মর্মমুখী দিক। অবশ্য মরমি ধারা প্রতিষ্ঠিত ধর্মের কাঠামোর বাইরেও থাকতে পারে। ইসলাম ধর্মের কাঠামোয় মর্মমুখী ধারা সুফিবাদ বা তাসাউফ; লৌকিক ভাষায় একে বলা হয় ফকিরি বা মারেফতপন্থা। আনুশাসনিক দিকটি হচ্ছে শরিয়ত। বলা যায়, ইসলামের জাহেরি বা বাইরের দিক নিয়ে কাজ করে শরিয়ত, আর সুফিবাদের সম্পর্ক বাতেনি বা ভিতরের দিকের সাথে। শরিয়তে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান-রীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু ধর্মে রূপক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুফিবাদ রূপকের আড়ালে নিহিত সত্যটিকে খোঁজে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় : ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি হলো হজ, আর হজের অন্যতম অনুষ্ঠান হলো মিনায় প্রতিষ্টিত তিনটি পাথরের স্তম্ভ — বড় শয়তান, মেঝ শয়তান ও ছোট শয়তানকে ৭টি করে কঙ্কর ছুঁড়ে মারা। হজের সময় সবাই অত্যন্ত উৎসাহ ও বিদ্বেষের সাথে এই কঙ্করগুলো ছুঁড়ে মারেন। শরিয়তের অনুষ্ঠান হিসেবে এটি একটি আবশ্যিক কর্ম, একে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু সুফি সাধক জানেন, হজরত একবার সাহাবিদের বললেন, “প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি করে শয়তান জুড়ে দেওয়া হয়েছে।” “ইয়া রাসুলুল্লাহ”, বললেন এক সাহাবি, “আপনার সাথেও কি শয়তান জুড়ে দেওয়া হয়েছে?” “হ্যাঁ, আমার সাথেও জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, আমি তাকে মুসলমান বানিয়ে ফেলেছি।” এই অন্তরের শয়তানকে মুসলমান বানানোই সুফির সাধনা। নিজের নফ্সে আম্মারা বা কলুষিত প্রবৃত্তির সাথে সংগ্রামই জেহাদে আকবর। নিজের ভিতরের পশুত্বকে উৎসর্গ করাই তার কোরবানি। হজরত যে-সকল শিক্ষা দিয়েছেন ও নির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে আপেক্ষিকতা আছে। পাত্রভেদে উপদেশ দেওয়া তাঁর নিয়ম। প্রখ্যাত সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা জানিয়েছেন, “রাসুলের কাছ থেকে আমি দু-ধরনের জ্ঞান লাভ করেছি; একটি আমি সবাইকে বলি, অন্যটি বললে আমার গলা কাটা যাবে।” এই যে কিছু সত্য আছে, রাসুলের সত্য, যা প্রকাশ্যে সবাইকে বলা যায় না, তা ধারণ করে সুফিবাদ। মাওলা আলি সম্পর্কে হজরত বলেছেন, “আমি জ্ঞানের শহর, আলি তার দরজা।” মাওলা আলি-কে প্রদত্ত এই যে গুপ্তজ্ঞান, সুফিসাধক এটা লাভ করতে চান। এই জ্ঞান সিনা-ব-সিনায় বা হৃদয় হতে হৃদয়ে পীরের মাধ্যমে পেতে হয়।
দেহে যে জৈবরাসায়নিক ও স্নায়বিক প্রবাহ রয়েছে তাকে জানা ও নিয়ন্ত্রণ করাটা সুফিসাধনার অংশ। দেহে কতগুলি লতিফা বা কেন্দ্র বা চক্র আছে যেগুলোতে মনোনিবেশ করতে হয়। গুরু সেগুলো চিনিয়ে দেন। গুরু আরও শিখিয়ে দেন জিকিরের বিভিন্ন পদ্ধতি। শরীর-ও-মন নিয়ন্ত্রণে জিকিরের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মনের স্তরগুলো সাধকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সচেতন মন থেকে অবচেতন হয়ে নির্জ্ঞান মনের সাথে পরিচিত হন সাধক। নিজের মনের অতল গহ্বরে যেসব বিষয় রয়েছে সেগুলো জানতে পারেন তিনি। অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর ও অপরূপ রূপকল্পগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনোদৈহিক অনেক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেন। আত্মপ্রত্যয় লাভ করেন সাধক। মন যখন স্থির হয় তখন মনের ওপারে নিভৃতে যে পরম বিদ্যমান তাঁর সাক্ষাৎ মেলে। সেই পরম আর সাধকের মধ্যে তখন কোনো ভেদরেখা থাকে না। তখন সাধক ভাবাবিষ্ট মনসুর হাল্লাজের মতো উপলব্ধি করেন : আনা-আল-হক (আমিই পরম সত্য), বায়েজিদ বোস্তামির মতো বুঝতে পারেন : আনা সুবহানি মা আজিমুশ শানি (আমি ভাসমান সত্তা, মহিমা কেবল আমারই), জুনায়েদ বোগদাদির মতো বলতে পারেন : লাইসা ফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ্ তাআলা (এই জোব্বার ভিতরে আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নাই)।
পবিত্র কোরান-এ বারবার তাগাদা দেওয়া হয়েছে : আকিমুস সালাতা। আরবি সালাত শব্দটির ফারসি প্রতিশব্দ হল নামাজ। কিন্তু সালাত শব্দটির অর্থ হল সংযোগ। অর্থাৎ, বলা হচ্ছে : সংযোগ প্রতিষ্ঠা কর। কার সঙ্গে সংযোগ? আল্লাহ্-র সঙ্গে। আল্লাহ কে? যিনি আমাদের সত্তার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিদ্যমান এবং যিনি সর্বসৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান এবং একমাত্র যিনি অস্তিমান। এই সংযোগ স্থাপনই সুফির প্রধান লক্ষ্য। কীভাবে এই সংযোগ স্থাপন করতে হয় এটা যে-গুরু শিখিয়ে দেন তিনিই পীর। সুফিবাদে পীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন; বলা যেতে পারে, সুফিবাদ মানে পীরপূজা — অর্থাৎ, পীরের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ। এই পীরপূজা প্রয়োজন কারণ পীরের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে হয়, যাকে ফানা ফিশ্ শায়েখ বলে। মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে en rapport বলা হয় তারই গভীরতম প্রযোগ এটা। পীরপূজা করতে হয় কারণ সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার প্রকাশ। একটি হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলছেন, “আমি ছিলাম গুপ্ত ভাণ্ডারে নিহিত; আমি প্রকাশিত হতে ইচ্ছে করলাম, সেজন্যই আমি এসব সৃষ্টি করলাম এবং প্রকাশিত হলাম।” আর সৃষ্টির মাঝে সেরা হল মানুষ; কাজেই মানুষেই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। আরেকটি হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ্ বলেছেন : মানুষ আমার রহস্য, আমি মানুষের রহস্য (আল ইনসানু সিররি, ওয়া আনা সিররুহু)। পীরের মধ্যে সেই পরমের প্রকাশ ঘটে, কারণ যিনি পরমের সাক্ষাৎ পেয়েছেন তিনিও হাকিকতে পরম হয়ে ওঠেন; অসীমের যে-কোনো অংশও অসীম — এ তো গাণিতিক সত্য। এ কারণেই বু-আলি শাহ কলন্দর বলে ওঠেন : পীরের সুরতে নবিকে দেখলাম, ওটা নবি নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ্ (বাশাকলে শায়েখে দিদাম মোস্তফারা, না দিদাম মোস্তফারা বালকে খোদারা); এ-কারণেই সাধক ঘোষণা করেন : পীরপূজাই সত্যপূজা (পীর পরস্তি হক পরস্তি), আর মোজাদ্দেদে আলফেসানি সেরহিন্দ শিক্ষা দেন : তোমার পীর তোমার প্রথম প্রভু (পীরে তাস্ত আউয়াল মাবুদ তাস্ত)। লালন সাঁইজির গানে এই পীরপূজার কথা বারবার পাই : ‘সহজ মানুষ ভজে দেখ না রে মন দিব্যজ্ঞানে’ বা ‘ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার/ সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার।’ পীরের অবয়ব ধ্যান করার মাধ্যমে নিজের দেহ-মনের আত্মবোধ হারিয়ে ফেলতে হয়। আমিত্ব ত্যাগের সাধনায় এই প্রক্রিয়া প্রয়োজন। আমিত্বই শয়তান। ইবলিশ শব্দটি এসেছে হিব্রু শব্দ বালাসা থেকে, যার অর্থ অহংকার। ‘আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে দিব্যজ্ঞানী সে হয়েছে।’– সাঁইজির এই বাণীটি একটি হাদিসে কুদসির অনুরূপ, যেটিতে সুফিবাদের সার তত্ত্ব পাওয়া যায় : মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু — অর্থাৎ, যে নিজের প্রবৃত্তিসমূহকে চিনেছে সে তার প্রভুকে চিনেছে। এই যে আত্মজ্ঞান অর্জনের সাধনা, পীরের তত্ত্বাবধানে এই সাধনার মাধ্যমে নিজের দেহমনের কার্যক্রম ও প্রবণতা, প্রবৃত্তির সকল উদ্বেলতা, আবেগের বিশাল উল্লাস, কল্পনার উদ্দাম ঝম্পন আর বাসনার বিপুল আকুতি এসব বাধ্যবাধকতা ক্রমে-ক্রমে অতিক্রম করতে পারেন সুফিসাধক।
সুফিসাধনার দেহতাত্ত্বিক কিছু ব্যাপার রয়েছে। রূপক ভাষায় বলা হয় : যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা-ই আছে দেহভাণ্ডে। সুফি পরিভাষায় মানবদেহকে আলম-ই-সগির বা ছোট বিশ্ব এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আলম-ই-কবির বা বড় বিশ্ব বলা হয়। মন ও পরমাত্মা বা রুহ এই দেহের মধ্যেই আছেন, তাই দেহকে মানসিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। দেহে যে জৈবরাসায়নিক ও স্নায়বিক প্রবাহ রয়েছে তাকে জানা ও নিয়ন্ত্রণ করাটা সুফিসাধনার অংশ। দেহে কতগুলি লতিফা বা কেন্দ্র বা চক্র আছে যেগুলোতে মনোনিবেশ করতে হয়। গুরু সেগুলো চিনিয়ে দেন। গুরু আরও শিখিয়ে দেন জিকিরের বিভিন্ন পদ্ধতি। শরীর-ও-মন নিয়ন্ত্রণে জিকিরের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মনের স্তরগুলো সাধকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সচেতন মন থেকে অবচেতন হয়ে নির্জ্ঞান মনের সাথে পরিচিত হন সাধক। নিজের মনের অতল গহ্বরে যেসব বিষয় রয়েছে সেগুলো জানতে পারেন তিনি। অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর ও অপরূপ রূপকল্পগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনোদৈহিক অনেক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেন। আত্মপ্রত্যয় লাভ করেন সাধক। মন যখন স্থির হয় তখন মনের ওপারে নিভৃতে যে পরম বিদ্যমান তাঁর সাক্ষাৎ মেলে। সেই পরম আর সাধকের মধ্যে তখন কোনো ভেদরেখা থাকে না। তখন সাধক ভাবাবিষ্ট মনসুর হাল্লাজের মতো উপলব্ধি করেন : আনা-আল-হক (আমিই পরম সত্য), বায়েজিদ বোস্তামির মতো বুঝতে পারেন : আনা সুবহানি মা আজিমুশ শানি (আমি ভাসমান সত্তা, মহিমা কেবল আমারই), জুনায়েদ বোগদাদির মতো বলতে পারেন : লাইসা ফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ্ তাআলা (এই জোব্বার ভিতরে আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নাই)।
প্রেম যে মানুষের এক মহৎ বৃত্তি তাতে কোনো দ্বিমত বোধহয় কারো নেই। কিন্তু সাধারণত এই প্রেম স্বার্থবিজড়িত থাকে। নারী-পুরুষের প্রেমে থাকে ভোগবাসনা, পিতা-মাতা-ভাই-বোন-সন্তানের প্রতি প্রেমে থাকে স্বার্থপরতা ও স্বজনপ্রীতি। কিন্তু নিষ্কাম ও সার্বজনীন প্রেমের চর্চার জন্যে এবং আত্মমুক্তির প্রক্রিয়াকে ফলবতী করার জন্যে গুরুর প্রতি ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি প্রেম সুফিবাদে গুরুত্বপূর্ণ। গুরুর সাথে ভক্তিনির্ভর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। ভক্তিভাবই প্রেমের পথে মুক্তির পথনির্দেশ করে। ভক্তিভাব অহম থেকে মুক্ত করে এবং মানবতাবোধের পরিধি বাড়িয়ে তোলে। এই প্রেমই সুফিকে সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ, শ্রেণিভেদ ও লিঙ্গবৈষম্যের ওপারে নিয়ে যায়। মোল্লা-পুরোহিত-পাদ্রীর মধ্যে ভেদবুদ্ধি থাকে, কিন্তু সাধকের মধ্যে তা থাকে না। রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা সুফিসাধকেরও কথা : যত মত, তত পথ। তিনিও মানেন : সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য : একজন পীরের কাছে অন্য যে-কোনো ধর্মাবলম্বী দীক্ষা নিতে পারেন তার নিজস্ব ধর্ম ত্যাগ না করেই। সুফিবাদের ঔদার্য ও সত্যনিষ্ঠার কারণেই এটা সম্ভবপর। ঋষির মতো সুফিও মানেন : সত্য একটি, সাধকেরা তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকেন।
ভক্তিভাব অহম থেকে মুক্ত করে এবং মানবতাবোধের পরিধি বাড়িয়ে তোলে। এই প্রেমই সুফিকে সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ, শ্রেণিভেদ ও লিঙ্গবৈষম্যের ওপারে নিয়ে যায়। মোল্লা-পুরোহিত-পাদ্রীর মধ্যে ভেদবুদ্ধি থাকে, কিন্তু সাধকের মধ্যে তা থাকে না। রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা সুফিসাধকেরও কথা : যত মত, তত পথ। তিনিও মানেন : সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।
দীর্ঘ সাধনার এক পর্যায়ে সব সংশয় অপসৃত হয়, অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত হয়। বিশেষ থেকে নির্বিশেষে পৌঁছান সাধক। আত্মস্বরূপ জানতে পারেন তিনি। প্রেম ও প্রজ্ঞার এই সাধনার জন্যেই পীরের কাছে বায়াত বা দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়, তাঁর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করতে হয়, তাঁর নির্দেশ মান্য করতে হয়। একেকবার ধ্যানসাধনার ৪১ দিন, কিংবা ১২০ দিন, কিংবা দীর্ঘতর সময় বিধি-নিষেধের মধ্যে থাকতে হয়। মৌন অবলম্বন, নিরামিষভোজন, দুই খণ্ড শেলাইবিহীন কাফনশুভ্র বস্ত্রধারণ করে দিন ও রাতের অধিকাংশ সময় পীরের ধ্যান, জিকির ও নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু অজিফা পাঠ করতে হয় নির্জনবাসের মাধ্যমে। সাধনার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। ক্রমে ক্রমে ঊর্ধ্বলোকে যেতে হয়। পীরভেদে ও সাধকভেদে সাধনার কার্যক্রম বিভিন্ন হতে পারে, তবে শারীরিক কৃচ্ছ্রতা, আত্মশুদ্ধি ও মোরাকাবা বা ধ্যান সুফিসাধনার মূলকথা।
নিজেকে জানবার তাগিদ দিয়েছেন সকল প্রজ্ঞাবান যুগে-যুগান্তরে। পৃথিবীর কোণে-কোণে চিরকাল সাধকেরা বিদ্যমান ছিলেন। আজও আছেন একালের সাধকেরা। সত্যের অম্বেষায় জাগতিক সকল সুখ ও বৈভব ও প্রতিষ্ঠা বিসর্জন দিয়ে কঠোর সাধনায় লিপ্ত থাকেন তাঁরা। বলখের বাদশাহ ইব্রাহিম বিন আদহাম ভগবান বুদ্ধের মতোই রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে অঙ্গে নিলেন ফকিরের মলিন বস্ত্র। সেকালের বিশ্বের সেরা বিদ্যাপীঠ নিজামিয়া মাদ্রাসার জাঁদরেল প্রিন্সিপাল ও খ্যাতনামা পণ্ডিত ইমাম গাজ্জালি নিরক্ষর আবু আলি ফরমাদির কাছে দীক্ষা নিয়ে পদ ও পাণ্ডিত্য, যশ ও প্রতিপত্তি, বিত্ত ও রাজানুগ্রহ সব ত্যাগ করে সুফিসাধকের কঠোর জীবন গ্রহণ করে দিন কাটালেন পর্যটনে ও আত্মনির্বাসনে ধ্যানমগ্নতায়। জালালুদ্দিন রুমি তাঁর অধ্যাপনা পরিত্যাগ করে পীর শামসে তাবরিজের সঙ্গে গূঢ় প্রেমখেলায় মেতে উঠলেন। আর এ-সবই পরম সত্যকে পাবার জন্য। সুফিবাদ সেই পরম সত্যে পৌঁছুবার সিরাতুল মুস্তাকিম।
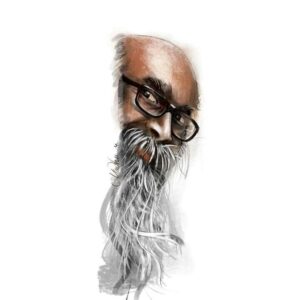


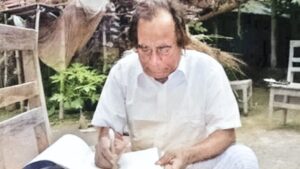


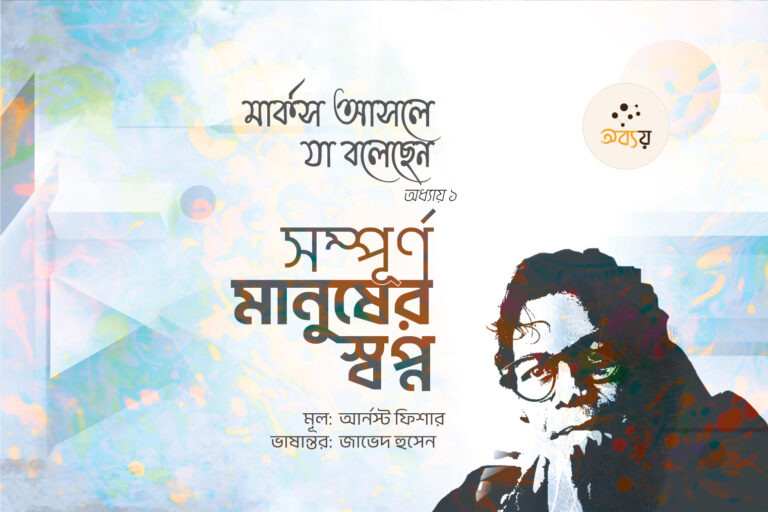
Leave a Reply