রাজু আলাউদ্দিন
রবীন্দ্রনাথ ‘১৪০০ সাল’ কবিতায় আত্মবিশ্বাসের সাথেই এক শ’ বছর পরের পাঠকদের সাথে তার সংযোগের বার্তা হিসেবে আনন্দ-অভিবাদন পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথে ওই রচনার পর, বহু আগেই একশ বছর পার হয়ে গেছে। অন্যদিকে, রবীন্দ্র্রনাথের মৃত্যুর এক শ’ বছর যদিও এখনও পার হয়নি, কিন্তু তিনি আজও পঠিত। হয়তো তার সব রচনা নয়, কিন্তু তার সমগ্র রচনার অনেক কিছুই আজও আমাদের পাঠহৃদয়কে আন্দোলিত করে। আমরা যদি আরও পেছন দিকে যাই, চলুন একেবারে বাংলা কবিতার গোড়াতেই খানিকটা ঘুরে আসা যাক। চর্যাপদের বয়স তো হাজার বছর হয়ে গেছে। হুবহু ওই ভাষায় আমরা এখন আর কথা বলি না, যেমন বলেন না ইংরেজরা শেক্সপিয়রের সেই পাঁচ শ বছর আগের ভাষায়। কিন্তু চর্যাপদের অনেক কবিতায় এমন সব হীরকোপম পংক্তি আছে যেগুলো আজও প্রাসঙ্গিক, যেমন “অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।” “উদকচান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা” ( জলে চাঁদ—সত্যি না মেকি), কিংবা “জো সো বোধি সোধ নিবুধী/ জো ষো চৌর সোই সাধী” ( যে বুদ্ধিমান সেই নির্বোধ বুঝো এটা অন্তরে/ আসলে যে সাধু লোকে ভুল বুঝে তাকে চোর বলে ধরে।) –এসব পংক্তি হাজার বছর উজিয়ে আমাদের কাছে আসতে পেরেছে এর বাচনিক গুণের কারণে। কথাগুলোর চিরকালীন আবেদন আমাদেরকে সমানভাবে স্পর্শ করে যায়। শেক্সপিয়রও তার নাটকগুলোয় এই চিরকালীন গুণ নিয়ে হাজির হন উত্তরকালের পাঠকদের কাছে—মানবস্বভাবের আরও বেশি জটিল, সর্বব্যাপী আর রহস্যময় ব্যাঞ্জনা নিয়ে। অথচ এই নাটকগুলো যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন এর স্রষ্টা ঘুণাক্ষরেও এগুলোর চিরকালীনতা সম্পর্কে ভাবেননি। সে যুগে লন্ডনে নাটক, অন্তত শেক্সপিয়রের নাটকগুলোকে সাহিত্য পদবাচ্যই মনে করা হতো না। শেক্সপিয়রের মৃত্যুর পর যখন বেন জনসন শেক্সপিয়রের নাট্যকর্মকে ‘সাহিত্য’ বলে অভিহিত করেছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবীরা তা নিয়ে হাসাহাসি করেছিলেন। গ্রিকরা নাট্যমাধ্যমকে যদিও বহু আগেই শিল্পের শীর্ষ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তখনও পর্যন্ত ইংল্যান্ডে নাটক শিল্পের মর্যাদা অর্জন করেনি। শেক্সপিয়রের নাটক তো নয়ই। কিন্তু ক্ষণকাল আর সমকালকে ফাঁকি দিয়ে শেক্সপিয়রের নাটকগুলো যে মহাকালের মহাসড়কে হাটতে শুরু করেছে সেটা বেন জনসন ঠিকই বুঝেছিলেন। Thou star of poets-এর রাজমুকুট পরিয়ে শেক্সপিয়র সম্পর্কে জনসন এও বলেছিলেন: Not for an age but for all time.
শেক্সপিয়রের চিরকালের হয়ে ওঠার কারণগুলো যে কী তা হয়তো অনেকেই অনেকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক সময় অনেক গৌণ কবিও দু একটি উজ্জ্বল পংক্তি লিখে ফেলতে পারেন। লিখেছেনও। তবে “একটি মাত্র উৎকৃষ্ট পংক্তি রচনা যতটা সহজ, বিশাল কোনো কাজে তা ফুটিয়ে তোলা তত সহজ নয়।” (–হোর্হে লুইস বোর্হেস)। বড় লেখকদের আশ্চর্য গুণ হচ্ছে এই যে তারা কেবল একটি দুটি কবিতার একটি দুটি পংক্তিতে নয়, তারা একটি রচনায় যেমন, তেমনি সমগ্র রচনায় ছড়িয়ে রাখেন সেই চিরকালীন আবেদনের সমুজ্জ্বল আবহ। গোটা রচনার মধ্যে তারা ক্ষণকালের তৃষ্ণা মিটিয়ে সর্বকালের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেন। শেক্সপিয়র তাই আমাদের কাছে চিরকালের হয়ে উঠেছেন।
শেক্সপিয়রের আগে গ্রীক নাট্যকাররা জীবনের অর্থহীনতা ও ধার্যবেদনাকে যে গভীরতায় প্রকাশ করেছেন অন্য কোনো ভাষার লেখকরা তেমনভাবে করেছেন কিনা সন্দেহ। সফোক্লিসের ‘রাজা ঔদিপাস’ ও ‘আন্তিগোনে’, ইউরিপিদেস-এর ‘হেকুবা’, এস্কাইলাসের ‘আগামেমনন’ ইত্যাদি নাটকে কাল ও মানবজাতির মধ্যে লোভ, হিংসা, প্রতিশোধ,ন্যায়বোধ, প্রতারণাসহ নৈতিকতার স্খলনগুলোকে কল্পনা ও বাস্তবতার মিশেলে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তা কেবল কাহিনীগুণেই নয়, বরং মানবস্বভাবের এমন কিছু শাশ্বত রূপকে তুলে ধরেছে যা আমাদেরকে আজও আলোড়িত করে। রাজা ঔদিপাস-এর ঘটনাটিকে আমরা কোনভাবেই মানতে পারি না কারণ তিনি মায়ের সঙ্গে অজান্তে এমন এক সম্পর্কে জড়িয়ে যান যা আমাদের নৈতিকতা ও প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু নাটকটি আমরা যখন পড়তে শুরু করি তখন ঘটনাপরম্পরার চৌম্বকীয় আকর্ষণ ও যৌক্তিক বিন্যাসের শিল্পকুশলতার কারণে পুরো ঘটনা এবং প্রধান পাত্রপাত্রী আমাদের সহানুভূতির কেন্দ্রে চলে আসে। নাটকের ইতিহাসে ঘটনাপরম্পরার এমন আশ্চর্য্য বিন্যাস দ্বিতীয় আর কোনো নাটকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঘটনাবলী এতটাই অনিবার্য কার্যকারণসূত্রে বাঁধা যে এর সামান্য পরিবর্তন বা বিকল্প কিছু ভাবার সুযোগ আমাদের জন্য তিনি রাখেননি। সংলাপের পারম্পর্য এতই অমোঘ আর পরবর্তীকালীন ঘটনা বা দৃশ্যের সঙ্গে এতই নিখুঁতভাবে বাঁধা যে অবিশ্বাস্য ও অকথ্য কাহিনীকেও দর্শক/পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সফোক্লিসের এই শৈল্পিক দক্ষতা বিস্ময়কর আর তাই আজও তিনি সমসাময়িক হয়ে আছেন।
যে-কোনো শিল্পকর্ম একেবারে ভিন্ন্ ভিন্ন কারণে উত্তরকালের পাঠকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কোনো কোনো শিল্পকর্ম শৈল্পিক নির্মাণের অনন্যতার কারণে, কোনো কোনো শিল্প কাহিনী বয়ানের শিল্পিত সৌকর্যের কারণে, কখনো কখনো মানবস্বভাবের স্বরূপ উন্মোচনের কারণে, কখনো বা বক্তব্যের শাশ্বত আবেদনের কারণে কালান্তরের কালপুরুষ হয়ে উঠতে পারেন।
মানবস্বভাবের স্বরূপ উন্মোচনের সূত্রে ইউরিপিদেস-এর ‘হেকুবা’ নাটকটির কথা আমাদের মনে না এসে পারে না। ট্রয়ের যুদ্ধে রানী হেকুবা ক্ষমতা হারিয়ে দাসে পরিণত হয়েছেন, যুদ্ধ তিনি প্রায় সব সন্তানকে হারিয়েছেন। এর পরও তিনি তার নৈতিকতাকে ধরে রেখেছেন। তার এই বিশ্বাস ছিল যে যে-কোনো প্রতিকূলতায় চরিত্রের ভালো দিকগুলো অটুট রাখা সম্ভব। যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও সর্বসান্ত হেকুবার তখনও পর্যন্ত একমাত্র ছোট্ট ছেলে পলিডোরাস বেঁচে ছিল, বাঁচার কারণ, হেকুবা ও রাজা প্রিয়ামের বড় মেয়ের জামাই এবং বন্ধু পলিমেস্টোরের কাছে ছেলেকে মূল্যবান সম্পদসহ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই বন্ধুর দায়িত্ব ছিল ওই সম্পদ ও সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখা যাতে করে যুদ্ধ শেষ হলে আবারও সন্তানের সাথে মিলিত হতে পারেন। একদিন হেকুবা থ্রেস নদীর তীর দিয়ে হাঁটার সময় একটা নগ্ন দেহ দেখতে পান। কাছে গিয়ে ভালো করে চেনার চেষ্টা করেন, কিন্তু মৃতদেহটিকে মাছ এমনভাবে খেয়ে ফেলেছে যে চেনার উপায় ছিল না। আরও কাছে গিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারেন এটি তার প্রিয় সন্তানের নিষ্প্রাণ দেহ। যে-বন্ধুকে বিশ্বাস করে একমাত্র জীবিত সন্তানকে সুরক্ষার জন্য হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সেই বন্ধু সম্পদের লোভে ছোট্ট ছেলেটিকে হত্যা করার পর মস্তক বিচ্ছিন্ন করে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। এই দৃশ্য তাকে আমূল বদলে দিয়েছিল। যে-নৈতিকতাকে সর্বতোভাবে রক্ষার চেষ্টা সে আজীবন করে এসেছে, তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এই বদলে-যাওয়া-হেকুবা এবার আরও সম্পদের লোভ দেখিয়ে পলিমেস্টোরকে নিয়ে এসে তার চোখ দুটো উপরে ফেলেন সন্তান হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে। হত্যা করা হয় পলিমেস্টোরের সন্তানকেও।
এই নাটকের প্রধান শক্তি কাহিনিতে নয়, বরং মানবস্বভাবের জটিলতা, লালসা, বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা, নিষ্ঠুরতা এবং বিয়োগান্তক বিধিলিপির অমোচনীয় স্বরূপ উন্মোচনে। গ্রীক সৃষ্টিশীল লেখকরা, বিশেষ করে নাট্যকাররা মানুষের বেদনাকে যতটা গভীর ও বিশ্বস্ততার সাথে প্রকাশ করতে পেরেছেন তা অন্য ভাষার সাহিত্যে প্রায় দুর্ভল। ‘ইলিয়াড’-এ আমরা তার এক সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি দেখতে পাই। মানবচরিত্র তাদের হাতে এমন দক্ষতায় রূপায়িত হয়েছে যা আমাদেরকে আজও মুগ্ধ করে। যা চিরকালের আবেদন নিয়ে হাজির হয় তা প্রাচীন হলেও আধুনিক। এ হচ্ছে চিরকালের আধুনিক।
‘ইলিয়াড’-এ আমরা তার এক সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি দেখতে পাই। মানবচরিত্র তাদের হাতে এমন দক্ষতায় রূপায়িত হয়েছে যা আমাদেরকে আজও মুগ্ধ করে। যা চিরকালের আবেদন নিয়ে হাজির হয় তা প্রাচীন হলেও আধুনিক। এ হচ্ছে চিরকালের আধুনিক।
ইতালো কালভিনো ‘Why Read the Classics?’ প্রবন্ধে আমাদেরকে চিরায়ত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এমন কিছু বলেছেন যা এই মুহূর্তে আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হতে পারে।
“একটি ক্লাসিকের প্রত্যেক পুনর্পাঠই প্রথম পাঠের মতো আবিষ্কারের এক অভিযান।”
(Every rereading of a classic is as much a voyage of discovery as the first reading. –The Literature Machine, P 127 )
“ ক্লাসিক হল এমন এক বই যার বক্তব্য কখনোই ফুরাবার না।”
(A classic is a book that has never finished saying what it has to say. –The Literature Machine, P 128)
“কাফকা পড়ার সময়, আমি “কাফকীয়” বিশেষণটির বৈধতা অনুমোদন করাকে যেমন এড়াতে পারি না, তেমনি তা প্রত্যাখ্যান করাকেও এড়াতে পারি না, যা নির্বিচারে ব্যবহৃত হওয়ায় ঘন্টায় প্রতি চারবার শুনতে হয়। আমি যদি তুর্গেনেভের ফাদারস অ্যান্ড সন্স বা দস্তয়েভস্কির দ্য পসেসড পড়ি, আমি না ভেবে পারি না, কিভাবে চরিত্রগুলি আমাদের যুগেও ভিন্ন রূপে আসছে।”
(When reading Kafka, I cannot avoid approving or rejecting the legitimacy of the adjective “Kafkaesque,” which one is likely to hear every quarter of an hour, applied indiscriminately. If I read Turgenev’s Fathers and Sons or Dostoyevsky’s The Possessed, I cannot help thinking how the characters have continued to be reincarnated right down to our own day. –The Literature Machine, P 128)
যে-সাহিত্য চিরকালের তা বুঝতে কালভিনো আমাদের জন্য এখানে অনেকটাই সহজ করে দিয়েছেন। স্মরণ করুন কাফকার একেবারেই ছোট্ট সেই গল্পটি কথা, ‘Before the law’ যা মনুষ্যরচিত আইনের বিচার থেকে একটি লোক পুরোপুরি বঞ্চিতই শুধু নয়, সে কোনদিনই, এমনকি বাদী হওয়ার সুযোগটুকুও পায় না। লোকটি আইনের দরজার সামনেই আমৃত্যু অপেক্ষা করে। মাত্র দেড় পৃষ্ঠার এই রূপকগল্পে কাফকা কেবল একটি যুগের নয়, বহু যুগের আইনি স্বভাবের খেয়ালি রূপটিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু এই গল্পে শুধু বক্তব্যই মুখ্য বিষয় নয়, এর শৈল্পিক বুননকৌশলও স্বচ্ছতা ও সংক্ষিপ্ততার গুণ নিয়ে অসামান্য হয়ে উঠেছে।
এসবের বিপরীতে ক্ষণকালের সাহিত্যের স্বরূপটা কী রকম? এরকম প্রশ্ন যদি আপনার মধ্যে কেউ উস্কে দেয় তাহলে আপনি এটুকু জানাতে পারেন: প্রধানত যা ক্ষণকালের রুচি ও অভ্যাসের অনুকূলে রচিত হয় এবং তাতেই যা তৃপ্ত বোধ করে, সেটাই ক্ষণকালের। ক্ষণকালের শিল্পের মধ্যে থাকে চমক দেয়ার প্রবণতা, চৌকশ হওয়ার শিশুতোষ টানটান ভান। মাঝেমধ্যে সে চটকদার দুএকটি পংক্তি হয়তো লিখে ফেলতে পারবে, কিন্তু বড় পরিসরে গিয়ে সে বিপুল বিশ্ব এবং মানবস্বভাবের রহস্যময় গোলকধাঁধা, সময় ও ইতিহাসের জটিল গ্রন্থিগুলো তার কাছে অদৃশ্যই থেকে যাবে। কারণ সে সীমিত পাঠ ও অভিজ্ঞতার ভেতরে বসবাস করে বলে এই পৃথিবীর অদৃশ্য বাস্তবতাকে কখনোই দেখতে পায় না। আর যদি বা ঘটনাক্রমে বা দৈবক্রমে খানিকটা দেখেও ফেলে, সেই দেখার অভিজ্ঞতাটাও রূপায়িত হয় দরিদ্র কলাকৌশলের মাধ্যমে। তার মধ্যে থাকে না জীবন ও কালের বিপুল বিস্ময়। তাদের মধ্যে ক্ষণিকের উদ্ভাস থাকলেও তা তাদের সমগ্র রচনায় পরিব্যাপ্ত নয়। তা দৈবাৎ এক অর্জন মাত্র। কিন্তু বড় শিল্পী তাদের রচনার প্রতি পৃষ্ঠায় বিরাট মনের অভিজ্ঞতা শৈল্পিক নকশায় উৎকীর্ণ করে তোলেন।
ক্ষণকালের সাহিত্যের স্বরূপটা কী রকম? এরকম প্রশ্ন যদি আপনার মধ্যে কেউ উস্কে দেয় তাহলে আপনি এটুকু জানাতে পারেন: প্রধানত যা ক্ষণকালের রুচি ও অভ্যাসের অনুকূলে রচিত হয় এবং তাতেই যা তৃপ্ত বোধ করে, সেটাই ক্ষণকালের।
গৌণ বা ক্ষণকালের সাহিত্যিক শিশুরা, এমনকি পরিণত বয়সেও অপরিণত রচনার প্রণেতা হিসেবেই বেঁচে থাকেন। রাশি রাশি ভারা ভারা রচনার বিপুল আয়তনে তারা ছোট্ট জিনিসকেই বড় করে দেখান। অন্যদিকে, একজন চিরকালের শিল্পী ছোট্ট পরিসরেও ফুটিয়ে তুলতে পারেন বিরাট এক পৃথিবীর রহস্য, কালের গোলকধাঁধা, মানবজীবনের সীমাহীন বিস্ময়কে।
যেমনটি একটু আগেই কাফকার ওই স্বল্পায়তনের রূপকগল্পটিতে দেখতে পেলাম। বাংলা ভাষায় জীবনানন্দ দাশ এই চিরকালীন শিল্পীর সবচেয়ে অক্ষয় এক উদাহরণ। তার প্রতিটি রচনার মধ্যে আছে এই জগত, জীবন ও কালের অপার রহস্য, বিস্ময় ও ভাষ্যের শিল্পিত উন্মোচন। তার অসংখ্য কবিতার সাথেই পাঠকদের নিবিড় পরিচয় থাকার কারণে আমার এই মূল্যায়নকে কেউ অস্বীকার করবেন না জানি। কিন্তু তার স্বল্পপঠিত কিন্তু কাফকার ওই “আইনের সামনে” শীর্ষক রূপকগল্পটির মতোই একটা ছোট্ট উদাহরণ দেবো যেখান জীবনানন্দ মহাজাগতিক চক্রাকার ধ্বংস ও বেদনাকে আশ্চর্য দক্ষতায় মূর্ত করে তুলেছেন।
কোথাও পাবে না শান্তি—যাবে তুমি এক দেশ থেকে দূরদেশে?
এ-মাঠ পুরানো লাগে—দেয়ালে নোনার গন্ধ—পায়রা শালিখ সব চেনা?
এক ছাঁদ ছেড়ে দিয়ে অন্য সূর্যে যায় তারা-লক্ষ্যের উদ্দেশে
তবুও অশোকস্তম্ভ কোনো দিকে সান্তনা দেবে না।
কেন লোভে উদ্যাপনা? মুখ ম্লান—চোখে তবু উত্তেজনা সাধ?
জীবনের ধার্য বেদনার থেকে এ-নিয়মে নির্মুক্তি কোথায়।
ফড়িং অনেক দূরে উড়ে যায় রোদে ঘাসে—তবু তার কামনা অবাধ
অসীম ফড়িংটিকে খুঁজে পাবে প্রকৃতির গোলকধাঁধাঁয়
ছেলেটির হাতে বন্দী প্রজাপতি শিশুসূর্যের মতো হাসে;
তবু তার দিন শেষ হয়ে গেল; একদিন হতই-তো, যেন এই সব
বিদ্যুতের মতো মৃদুক্ষুদ্র প্রাণ জানে তার; যতো বার হৃদয়ের গভীর প্রয়াসে
বাঁধা ছিঁড়ে যেতে চায়—পরিচিত নিরাশায় তত বার হয় সে নীরব।
অলঙ্ঘ্য অন্তঃশীল অন্ধকার ঘিরে আছে সব;
জানে তাহা কীটেরাও পতঙ্গেরা শান্ত শিব পাখির ছানাও।
বনহংসীশিশু শূন্যে চোখ মেলে দিয়ে অবাস্তব
স্বস্তি চায়;—হে সৃষ্টির বনহংসী, কী অমৃত চাও? (দেশ কাল সন্তনি)
এই কবিতাটি এক মহৎ শিল্পীর এমন এক রচনা যা যে-কোনো জাতির, যে-কোনো কালের পাঠকের চিত্তকে মহাজাগতিক বোধের অংশিদার করে তুলবে।

কবি, লেখক ও অনুবাদক।


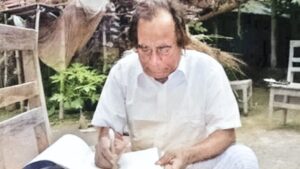

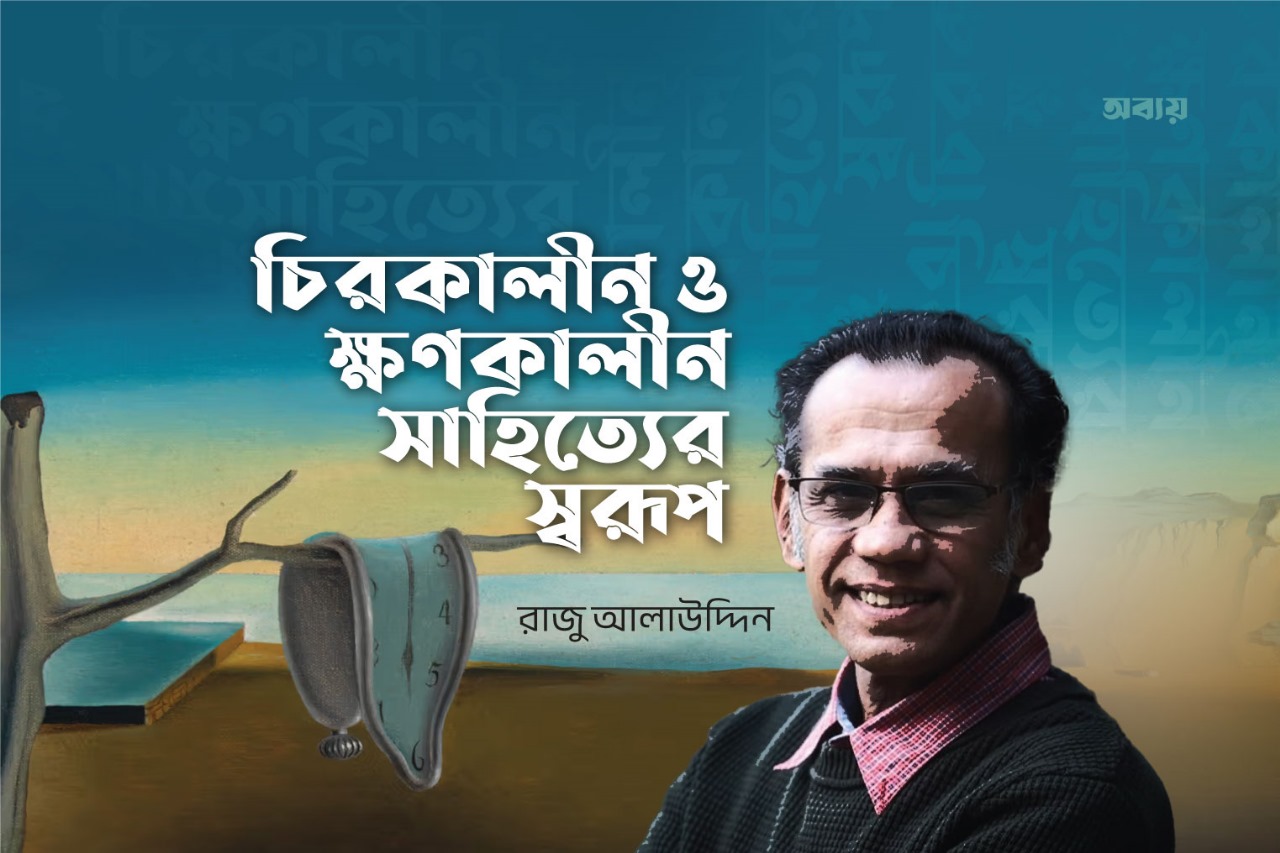

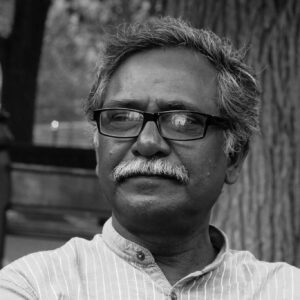
Leave a Reply