।।সম্পূর্ণ মানুষের স্বপ্ন।।
মূল আর্নস্ট ফিশার
ভাষান্তর: জাভেদ হুসেন
মার্কসের সারা জীবনের কাজের প্রেরণা ছিল “সম্পূর্ণ মানুষের স্বপ্ন”। সেই স্বপ্ন এক সংহত মানুষের, যা সংহত মানবিকতার ভিত্তি, যে ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের ভেতরে বাস করা মানবিকতা বাস্তব হয়ে উঠবে। মানুষের ভেতরে থাকা এই সম্ভাবনার বাস্তবায়নকে মার্কস মানব মুক্তির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন। তার জন্য মানুষকে বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করে যেতে হবে। এই বিচ্ছিন্নতা নিজের সঙ্গে নিজের আর একের সঙ্গে আরেকজনের। এর জন্য দরকার সংকীর্ণ অর্থনৈতিক স্বার্থের দৌড় হতে মানবতার মুক্তি আর বিস্তীর্ণ সৃজনশীলতার জগৎ উন্মোচন। ফিশার দেখাচ্ছেন যে, মার্কসের দৃষ্টিতে এই মানবতা তাঁর ধর্ম ও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির আলোচনার ধরন, দুইয়ের মাঝেই স্পষ্ট। -ফস্টার
সারা জীবনে মার্কসের চিন্তা বিভিন্ন রকম পথ পার হয়েছে। তবে যেখান থেকে তিনি চলা শুরু করেছেন, তা ছিল অটুট। সেটা হলো সম্পূর্ণ, সমগ্র মানুষের সম্ভাবনা।
অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে শিল্প বিপ্লব এবং পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিজয় ঘটল। সেই থেকে শ্রম বিভাজন, যান্ত্রিকায়ন, শোষণ আর বাণিজ্যের মাধ্যমে মানুষকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে ফেলা ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার মৌলিক অংশ হয়ে গেছে। যেসব মানুষ মানবিক বোধ আর ভাবনা লালন করেন, তাদের সবার মাঝে এক জায়গায় মিল আছে। তারা সবাই নিজের সত্তার সাথে, নিজের প্রজাতির সাথে আর প্রকৃতির সাথে ঘটে যাওয়া বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করে ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন।
যে জগৎ সবকিছুকে পণ্য আর মানুষকে জিনিসের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে, তার বিরুদ্ধে রোমান্টিক বিদ্রোহে লৌহযুগের কবি আর দার্শনিকদের অনেক অভিযোগ আছে। যেমন-মানুষ নিজেরই সত্তার খণ্ডিত অংশ হয়ে গেছে, তার নিজেরই কাজের তলায় সে চাপা পড়ে গেছে, চলে গেছে নিজের কাছ হতে অনেক দূরের নির্বাসনে।
শ্রম হতে আনন্দের, উপায় হতে লক্ষ্যের, উদ্যোগ হতে ফলাফলের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। সমগ্রের একটা ছোট অংশের শেকলে অন্তহীন বন্দিত্বে বাঁধা পড়ে মানুষ নিছক একটা টুকরো হয়ে বেড়ে উঠেছে। তার কানে আসে তারই চালু করা যন্ত্রের অন্তহীন একঘেয়ে আর্তনাদ। নিজ অস্তিত্বের ছন্দ আর তার কখনোই মেলানো হয় না। নিজ স্বভাবের ওপর মানবিকতার মোহর মারার বদলে সে যা হয়ে ওঠে তা নিজ পেশা বা নিজের বিশেষ জ্ঞানের ছাপের বেশি কিছু নয়।
(Fredrich Schiller, On the Aesthatic Education of Man)
কৃৎকৌশল আর শিল্পের অবাধ্য উন্নয়ন, লোভ আর বেনিয়া মরমের সর্বগ্রাসিতা, পুঁজি আর সর্বহারার দুর্দশার বাড়-বাড়ন্ত, বিপ্লবের আশা আর বিপ্লব পরবর্তী বাস্তবতার হতাশার কাল জন্ম দিয়েছিল প্রসন্ন-মুখ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে রোমান্টিক প্রতিবাদ। বুর্জোয়া জগতের বিরোধী অভিজাত আর জনসাধারণ-দুই পক্ষই এই প্রতিবাদে যোগ দিয়েছিল। দুই পক্ষই প্রগতিশীল শ্রম বিভাজনের হাতে মানুষের বিমানবিকীকরণের নিন্দা জানাচ্ছিল। এই বিভাজনের চূড়ান্ত ফল ছিল সমাজের একদিকে অন্তহীন সম্পদ বৃদ্ধি, আরেক দিকে অশেষ বস্তুগত আর মরমি লাঞ্ছনা। তবে সময়ের সঙ্গে রোমান্টিক আন্দোলনে বিভেদ ঘটল। কেউ কেউ বললেন যে, অতীতই পরিত্রাণের একমাত্র উৎসমুখ, তাদের কাছে মনে হলো সেই সময়ই মানুষের অখণ্ডতা আর মর্যাদা ছিল। আরেক দল মুখ ফেরালেন ভবিষ্যতের দিকে, স্বপ্ন দেখলেন অনাগত মুক্তি, প্রাচুর্য আর মানবিকতার রাজ্যে সমগ্র মানুষের বিদ্রোহের।
আমেরিকা আর ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিপ্লব মানুষের স্বাধীনতার অধিকারের- “স্বাধীন ব্যক্তিত্বের” ঘোষণা দিয়েছিল। এই ঘোষণা আর তার পরের বাস্তবতা অনেককেই দুঃখ দিয়েছিল। বুর্জোয়া সমাজে মানুষ আদতেই ব্যক্তি হয়ে উঠেছিল। তবে তা জনসমাজে অপর মানুষের মাঝে নয়, সে ব্যক্তি হয়ে উঠেছিল সমাজে অপর মানুষের বিরুদ্ধে তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হতে। তরুণ মার্কস লিখছেন, “মানুষের অধিকার হিসেবে স্বাধীনতা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এর ভিত্তি বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতা।’
মানুষের অনুমিত এই সব অধিকারের কোনটিই তাই অহংসর্বস্ব মানুষ, সিভিল সমাজের সদস্য হিসেবে যেমন আছে তেমন মানুষের গণ্ডীর বাইরে যেতে পারে না: মানে, এ এক এমন ব্যক্তি যে তার সম্প্রদায় হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের মাঝেই গুটিয়ে আছে, নিজের ব্যক্তি স্বার্থে আপাদমস্তক মগ্ন হয়ে নিজ ব্যক্তি ঝোঁকে যা করার তা করে যাচ্ছে।
অতএব সমস্যাটা হলো ফাঁপা ব্যক্তিকতায় নামিয়ে আনা, নিখাদ ব্যক্তিস্বার্থে মজে সম্পূর্ণ থাকা মানুষকে, মানে ব্যক্তিকে জনসমাজের সাথে এক করা। এই এক করার ভিত্তি হবে মুষ্টিমেয়র প্রাধান্য নয়, বরং সকলের মুক্তি।
একুশ বছর বয়সে মার্কস বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট করেন। এই জন্য তিনি কিছু নোট তৈরি করেন। এই নোটগুলোতে তখনো তিনি শ্রেণিসংগ্রাম, সর্বহারা ও বিপ্লব, শাসকহীন শ্রেণিহীন সমাজে “মুক্তির রাজত্বের” কথা বলার জায়গায় পৌঁছাননি। তবে তাঁর ছয় নম্বর নোটবুকে এপিকিউরীয় এবং স্টোইক দার্শনিকদের মৌলিক আত্মকেন্দ্রিকতা প্রসঙ্গে এই কথাগুলো পাওয়া যায়: “এভাবে, যখন সর্বব্যাপী সূর্য অস্ত যায়, তখন কি পতঙ্গ ব্যক্তিকতার দীপশিখা খোঁজে!” এরও আগে তিন নম্বর নোটবুকে লিখছেন: “যে নিজের শক্তিতে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করায়, নিজের খোলসের ভেতরে অন্তহীন ঘুরপাক খাওয়ার বদলে জগৎস্রষ্টা হওয়াতে আনন্দ পায় না, তার ওপর মরম অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করেছে।” আর পরে সপ্তম নোটবুকে:
এক্তিয়ার আর শুভবিশ্বাসের জোরে কি আদতেই কোন দর্শনকে দর্শন হিসেবে মেনে নিতে হবে, হোক না সে এক্তিয়ার গোটা জাতির আর সেই বিশ্বাস শত বছরের পুরনো!
মার্কসের কাছে “সর্বব্যাপী সূর্য” মানে ছিল সাধারণ লক্ষ্যের জন্য ব্যক্তির অঙ্গীকার, জনস্বার্থে তার অংশগ্রহণ, তার ভাবনা আর কাজের সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ ছাপিয়ে যাওয়া। মার্কস “নিজের খোলসের ভেতরে অন্তহীন ঘুরপাক” খেতে অস্বীকার করে “জগৎস্রষ্টা” হতে চেয়েছেন। আর তার মানে জগৎকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নিজের করে নিয়ে এর বস্তুগত রূপান্তরে অবদান রাখা। নতুন এক সামাজিক ঊষার আকাঙ্ক্ষা, এমন এক “সর্বব্যাপী” সূর্যের বাসনা যার সামনে ব্যক্তিকতার প্রদীপ নিষ্প্রভদেখাবে, এখানে তা স্পষ্ট চোখে পড়ে। তবে সমানভাবে নজরে পড়ছে যে এখানে এক পর্যালোচক মন আছে যে কেবল এক্তিয়ার আর শুভবিশ্বাসের জোরে কোন দর্শন, তত্ত্ব বা পদ্ধতিকে সত্য বলে মানতে নারাজ। একুশ বছর বয়সেই মার্কস নতুন সার্বিকতার দিকে পথ চলতে, নতুন জগতের স্রষ্টা হতে প্রস্তুত হয়ে গেছেন। আর তার জন্য যা কিছু আছে বা হবে তাকে পর্যালোচনামূলকভাবে আবার যাচাই করে দেখার অধিকার তিনি ছাড়তে নারাজ।
বার্লিনে মার্কস আইন, দর্শন এবং ইতিহাস পড়ছিলেন। সেখানে ছিল হেগেলের ভাবনার রাজত্ব, তরুণ পণ্ডিত আর চিন্তকদের মাঝে তার আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। তার বিপুল দার্শনিক রচনাবলি একই সঙ্গে রোমান্টিকবাদের শিখরচূড়া আর তার অস্বীকৃতি। হেগেল বিশ্ব ইতিহাসের মাঝে বিশ্ব মরমকে প্রতিটি বিচ্ছিন্নতার ধারাবাহিক রূপকে পার হয়ে যেতে দেখেছেন। নিজ সত্তা হতে দূরে সরে যাওয়া, আবার নিজ সত্তার মাঝে ফিরে আসার পুনর্মিলন-এভাবে সত্তার নিজের সাথে অচেতন মিলন হতে সচেতন মিলন ঘটার অগ্রগতি সাধিত হয়। হেগেলের দর্শনের জটিলতা আসলে তার কালের পরস্পরবিরোধী গতিশীলতার প্রকাশ। এর মাঝে আছে বিকাশের ধারণা, মুক্তি আর প্রাচুর্যের স্বপ্ন আর নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠা এক বাস্তবতা।
তরুণ মার্কস প্রথমে হেগেলকে খারিজ করেছিলেন। তারপর শীঘ্রই আবার এই বিশাল দার্শনিক আর তাঁর দ্বান্দ্বিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই দ্বান্দ্বিকতার প্রতি তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। সেই দ্বান্দ্বিকতার মানে চিন্তা আর সব জিনিসের স্বভাবের মাঝের অন্তর্গত স্ববিরোধ। এর মানে এই যে, কোন কিছুকে আলাদা করে বা কার্য আর কারণের সরলরৈখিক পরম্পরা হিসেবে দেখলে কিছুই বোঝা যাবে না। একে বোঝা যাবে কেবল সমস্ত ফ্যাক্টরের বহুমুখী মিথস্ক্রিয়া এবং নিজেরই সাথে দ্বন্দ্বরত হিসেবে। সমস্ত কিছুই অস্তিত্ববান হওয়ার সাথে নিজের অস্বীকৃতিকেও উৎপাদন করে এবং এর বিকাশ যেদিকে এগিয়ে যায় তা হচ্ছে অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি। এই ধারণার যে ফলাফল মার্কস টানলেন তা হেগেলকে পার হয়ে বহুদূর এগিয়ে গেল।
১৮৪২ থেকে ১৮৪৩ সালে মার্কস ছিলেন উদার সংবাদপত্র রেইনিশ সাইটুং-এর সম্পাদক। মার্কসের র্যাডিকেল-গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সেই সময়ের জার্মান শাসকদের গলার কাঁটা হয়ে উঠল। ফলে তাকে জার্মানি ছেড়ে প্যারিসে চলে আসতে হলো। ১৮৪৪ সালে তিনি জার্মান-ফরাসি বর্ষপঞ্জিতে ছেড়ে আসা জার্মানির অবস্থা এমনভাবে বয়ান করছেন:
একটা বিচলন নিয়ে জার্মান ইতিহাস তৃপ্তি পায়, ইতিহাসের নভোমণ্ডলে কোন জাতি জার্মানির আগে সেই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে আসেনি, জার্মানির পরেও যাবে না। কেননা আধুনিক জাতিগুলোর রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠাগুলোতে আমরা শরিক, যদিও তাদের বিপ্লবগুলোতে আমরা শরিক হইনি। আমরা রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে গিয়েছি, তার প্রথম কারণ অন্যান্য জাতি বিপ্লব ঘটাবার সাহস করেছে, আর দ্বিতীয় কারণ অন্যান্য জাতি প্রতিবিপ্লবে বিড়ম্বিত হয়েছে, প্রথমবার আমাদের শাসকেরা ভীত ছিল বলে, আর দ্বিতীয়বার আমাদের শাসকেরা ভীত ছিল না বলে। আমরা এবং সর্বাগ্রে আর সর্বোপরি যাঁরা আমাদের
চরান-কখনো স্বাধীনতার সংসর্গে পড়িনি, একবার ছাড়া-সেটার সমাধির দিন।
প্যারিসে মার্কসের সঙ্গে দেখা হলো রাইনল্যান্ডের কারখানা মালিকের ছেলে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের সঙ্গে। এঙ্গেলস তখন লন্ডনে কাজ করেন। এই পরিচয়ের ফলে মার্কস সেই সময়ের সবচেয়ে অগ্রসর শিল্পোন্নত দেশের বহাল সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারলেন। সেই সাথে মার্কস পেলেন এমন এক বন্ধু, যার নজির ইতিহাসে অল্পই পাওয়া যায়। সেই অনন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অসাধারণ প্রতিভার স্বীকৃতি এঙ্গেলস দিয়েছেন লেশমাত্র ঈর্ষা প্রদর্শন না করে। এঙ্গেলস মার্কসের বুদ্ধিবৃত্তিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে নিবেদিতপ্রাণ সাথী হলেন, সেই সাথে বার বার তাঁর ব্যক্তিজীবনের পরিত্রাতা হয়েও দেখা দিয়েছেন। মার্কসবাদে এঙ্গেলসের দার্শনিক অবদান নিয়ে কেউ হয়তো ভিন্ন কথা বলতে পারেন, কিন্তু তাঁদের মাঝের জীবনব্যাপী উর্বর বন্ধুত্ব সমস্ত সমালোচনার উর্ধ্বে।
প্যারিসে মার্কস সর্বহারাদের সম্পর্কে জানতে পারলেন।
সর্বহারাকে তিনি দেখলেন বিমানবিকীকরণের, সমস্ত দুর্দশার চূড়ান্ত হিসেবে। রোমান্টিকরা একে দেখতেন মানব স্বভাবের অপলাপ হিসেবে। মার্কস কিন্তু এই চূড়ান্ত নেতিকরণের মাঝেই একে অতিক্রমের আশা খুঁজে পেলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সর্বহারা তাদের দারিদ্র্যের কারণেই, সেই দারিদ্র্যের কারণগুলোর মূল ভিত্তি উপড়ে ফেলে নিজেদের অমানবিক অবস্থা হতে মুক্তি ঘটাবে। আর নিজেদের মুক্তি অর্জনের সঙ্গে তারা মানব জাতিরও মুক্তিদানকারী হয়ে উঠবে।
তাঁর কালের সর্বহারাদের মাঝে যে মানবিক অস্বীকৃতি তিনি দেখেছেন, মার্কস তার বর্ণনা দিয়েছেন অসাধারণ তীক্ষ্ণতার সঙ্গে।
এটা সত্য যে, শ্রম ধনীর জন্য বিস্ময়কর সব জিনিস উৎপাদন করে- কিন্তু শ্রমিকের জন্য সে উৎপাদন করে বঞ্চনা। প্রাসাদোপম অট্টালিকা সে তৈরি করে, অথচ তার নিজের জায়গা হয় জরাজীর্ণ বস্তিতে। সৌন্দর্য উৎপাদন করে শ্রমিকের ভাগে পড়ে কদর্যতা। সে যন্ত্র দিয়ে শ্রমকে প্রতিস্থাপন করে, কিন্তু তা করতে গিয়ে শ্রমিকদের একাংশ ফিরে যায় বর্বর ধরনের শ্রমে, আরেকটা অংশ যন্ত্রে পরিণত হয়। বুদ্ধিমত্তার উৎপাদন করে শ্রমিকদের ভাগে পড়ে মূঢ়তা, মানসিক বিকলাঙ্গতা।
শ্রম ধনীর জন্য বিস্ময়কর সব জিনিস উৎপাদন করে- কিন্তু শ্রমিকের জন্য সে উৎপাদন করে বঞ্চনা। প্রাসাদোপম অট্টালিকা সে তৈরি করে, অথচ তার নিজের জায়গা হয় জরাজীর্ণ বস্তিতে। সৌন্দর্য উৎপাদন করে শ্রমিকের ভাগে পড়ে কদর্যতা। সে যন্ত্র দিয়ে শ্রমকে প্রতিস্থাপন করে, কিন্তু তা করতে গিয়ে শ্রমিকদের একাংশ ফিরে যায় বর্বর ধরনের শ্রমে, আরেকটা অংশ যন্ত্রে পরিণত হয়। বুদ্ধিমত্তার উৎপাদন করে শ্রমিকদের ভাগে পড়ে মূঢ়তা, মানসিক বিকলাঙ্গতা।
সর্বহারা তার কাজের মাঝে নিজেকে পূর্ণ না করে নিজেকেই প্রত্যাখ্যান করে,
কাজের মধ্যে শ্রমিক নিজেকে স্বীকৃতির বদলে অস্বীকৃতিই জানায়, তৃপ্তির বদলে অতৃপ্তি বোধ করে, দৈহিক ও মানসিক শক্তির সুষ্ঠু ও স্বাধীন বিকাশ তো দূরের কথা, দেহমনকে তিলে তিলে ধ্বংস করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। শ্রমিক তাই নিজেকে তার কাজের বাইরে বলে অনুভব করে; আবার কাজের ক্ষেত্রে কাজটাকে অনুভব করে নিজের বাইরে বলে। যতক্ষণ সে কাজ করে না ততক্ষণ সে স্বস্তি বোধ করে; আর যখন সে কাজ করে তখন সে স্বস্তি হারায়।
সন্দেহ নেই যে, সৃচিতীক্ষ্ণ মন্তব্য করতে মার্কস সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তবে সর্বহারাদের দুর্দশা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি যে কিছু বাড়িয়ে বলেননি, সমকালীন নথিপত্রে এর প্রমাণ আছে। সেই বিশাল দার্শনিকের র্যাডিকেল শিষ্য তরুণ হেগেলীয়রা আশা করেছিলেন যে, নাস্তিকতা অপর জগৎ হতে মানুষের মরমকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে এনে তাকে মুক্তি দেবে। মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আরো গভীর। ধর্মের পর্যালোচনা তাঁর কাছে ছিল “সকল পর্যালোচনার সিদ্ধান্তসূত্র”। তবে তিনি বস্তুগত শৃঙ্খলের সঙ্গে সঙ্গে মরমি শৃঙ্খল হতে মুক্তির ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন। ধর্মকে তিনি দেখেছেন দুইভাবে- “বাস্তব দুর্দশার প্রকাশ” এবং “বাস্তব দুর্দশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ” হিসেবে।
ধর্ম হলো নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, ঠিক যেমন সেটা হলো আত্মাবিহীন পরিবেশের আত্মা। ধর্ম হলো জনগণের জন্য আফিম।
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা ঘটে, এই প্রেক্ষাপটে মার্কস আসলে কী বলেছেন খুব বেশি মানুষ সে সম্পর্কে সচেতন নয়। এই উদ্ধৃতি সাধারণত এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে মনে হয় যে ধর্ম মানুষের জন্য আফিমের মত বিষবৎ কিছু, বাইরের কেউ এই মাদক মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে। উদ্ধৃতির আগের অংশ এড়িয়ে যাওয়া হয়।
অবাস্তবতার অস্বীকৃতি হিসেবে নাস্তিকতা আর কোন অর্থ বহন করে না, কারণ নাস্তিকতা হচ্ছে ঈশ্বরের নেতিকরণ, আর এই নেতিকরণের মাঝ দিয়েই মানুষের অস্তিত্ব স্বীকার্য করে নেয়া। কিন্তু সমাজতন্ত্র হিসেবে সমাজতন্ত্রের আর এমন কোন ঘুরপথের দরকার হয় না। সে সারসত্তা হিসেবে মানুষ এবং প্রকৃতির তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক সংবেদনগত চৈতন্য হতে যাত্রা শুরু করে। সমাজতন্ত্র হলো মানুষের সদর্থক আত্মচৈতন্য, যার আর ধর্মকে উৎখাত করার মধ্যস্থতার দরকার পড়ে না। ঠিক যেমন বাস্তব জীবন হলো কমিউনিজমের মাধ্যমে মানুষের সদর্থক বাস্তবতা, যা আর ব্যক্তি সম্পত্তি উৎখাতের মধ্যস্থতাকৃত নয়। নেতিকরণের নেতিকরণ হিসেবে কমিউনিজম হলো সদর্থক ধরন, আর তাই তা সেই বাস্তব স্তর, যা প্রয়োজন মানবমুক্তি এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়াতে ঐতিহাসিক বিকাশের পরবর্তী স্তরের জন্য। কমিউনিজম হলো তাৎক্ষণিক ভবিষ্যতের আবশ্যকীয় আঙ্গিক এবং গতিশীল নীতি, কিন্তু এমন কমিউনিজম মানব বিকাশের লক্ষ্য, মানব সমাজের আঙ্গিক নয়।”
শ্রম হতে আনন্দের, উপায় হতে লক্ষ্যের, উদ্যোগ হতে ফলাফলের” বিচ্ছেদ ঘটিয়েই ক্ষান্ত হয় না। সর্বহারা এখানে যন্ত্র, মুনাফা আর দারিদ্র্যের জগতের টুকরো হওয়া, সংযোগহীন, ভাড়াটে স্বভাবের সবচাইতে চূড়ান্ত প্রকাশ। অস্বীকৃতি যত স্পষ্ট হয়, যে জিনিসকে অস্বীকার করা হচ্ছে তাও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। আর সেই স্পষ্টতর জিনিসটা হচ্ছে অবাস্তবায়িত মানুষের ছবি।
আমরা দেখতে পাব যে মার্কসের কাছে ধর্ম, নাস্তিকতা, আর কমিউনিজম সম্পূর্ণ বিকাশের লক্ষ্য নয়, বরং এর স্তর বা বৈশিষ্ট্য। লক্ষ্য হচ্ছে পজিটিভ মানবতাবাদ, মানুষের বাস্তব জীবন। সর্বহারার অস্তিত্ব এমন জীবনের সবচাইতে লক্ষণীয় স্ববিরোধ। কিন্তু “শিল্পের বিস্ফোরিত বাস্তবতা” নিজেকে কেবল সর্বহারাতেই প্রকাশ করে এমন নয়। পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করলে যা উঠে আসে তা শিলার যা ধারণা করেছিলেন তার চাইতে শতগুণ ভয়াবহ। সে কেবল “শ্রম হতে আনন্দের, উপায় হতে লক্ষ্যের, উদ্যোগ হতে ফলাফলের” বিচ্ছেদ ঘটিয়েই ক্ষান্ত হয় না। সর্বহারা এখানে যন্ত্র, মুনাফা আর দারিদ্র্যের জগতের টুকরো হওয়া, সংযোগহীন, ভাড়াটে স্বভাবের সবচাইতে চূড়ান্ত প্রকাশ। অস্বীকৃতি যত স্পষ্ট হয়, যে জিনিসকে অস্বীকার করা হচ্ছে তাও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। আর সেই স্পষ্টতর জিনিসটা হচ্ছে অবাস্তবায়িত মানুষের ছবি।
ধর্মের যাত্রাবিন্দু হচ্ছে ঈশ্বর। হেগেলের যাত্রাবিন্দু রাষ্ট্র। মার্কসের মানুষ। হেগেলের অধিকার দর্শনের পর্যালোচনায় মার্কস লিখছেন:
হেগেল যাত্রা শুরু করেন রাষ্ট্র হতে আর মানুষকে বিষয়ীভূত রাষ্ট্র বানিয়ে ফেলেন। গণতন্ত্র যাত্রা শুরু করে মানুষ হতে আর রাষ্ট্রকে বানায় বিষয়ভূত মানুষ… মানুষ আইনের খাতিরে অস্তিমান থাকে না, আইন মানুষের জন্য অস্তিমান থাকে: এ হলো মানব অস্তিত্ব, যেখানে কিনা অন্য মানুষের জন্য তা হলো আইনি অস্তিত্ব। এই হলো গণতন্ত্রের মৌলিক ফারাক।
ধর্মের যাত্রাবিন্দু হচ্ছে ঈশ্বর। হেগেলের যাত্রাবিন্দু রাষ্ট্র। মার্কসের মানুষ। হেগেলের অধিকার দর্শনের পর্যালোচনায় মার্কস লিখছেন:
হেগেল যাত্রা শুরু করেন রাষ্ট্র হতে আর মানুষকে বিষয়ীভূত রাষ্ট্র বানিয়ে ফেলেন। গণতন্ত্র যাত্রা শুরু করে মানুষ হতে আর রাষ্ট্রকে বানায় বিষয়ভূত মানুষ… মানুষ আইনের খাতিরে অস্তিমান থাকে না, আইন মানুষের জন্য অস্তিমান থাকে: এ হলো মানব অস্তিত্ব, যেখানে কিনা অন্য মানুষের জন্য তা হলো আইনি অস্তিত্ব। এই হলো গণতন্ত্রের মৌলিক ফারাক।
মার্কসের কাছে নির্ণায়ক জিনিসটা কেবল “সার্বিক”, নিজেই নিজের লক্ষ্য এমন কোন ব্যবস্থা নয়। তার নির্ণায়ক হচ্ছে বরং মানুষ-মূর্ত, বাস্তব, ব্যক্তি মানুষ। তাঁর চিন্তার, সমস্ত চেষ্টার বিষয় হচ্ছে সম্পূর্ণ মানুষ, মানুষের বাস্তবতা, ইতিবাচক মানবতা।
মুক্ত ব্যক্তি হয়ে বিকশিত হতে মানুষের জনসমাজ প্রয়োজন। “জনসমাজের পূর্ববর্তী বিকল্পগুলোতে, রাষ্ট্র, ইত্যাদিতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল কেবল সেই ব্যক্তিদের জন্য, যারা এই শাসকশ্রেণির সঙ্গে সম্পর্কে বেড়ে উঠেছে। আর তাদের ঐ শ্রেণির সদস্য না থাকলে সেই স্বাধীনতাও আর থাকত না।” যেসব ব্যক্তি স্বাধীন হওয়ার ভান ধরত, তারাও আসলে কেবল তাদের সম্পূর্ণ সামাজিক বিকাশের (ভাষা, ঐতিহ্য, বেড়ে ওঠা ইত্যাদি) হাতেই যে শর্তাবদ্ধ তাই নয়, সেই সাথে তাদের শ্রেণি, সম্পত্তি বা পেশাও শর্ত হিসেবে কাজ করত। তাদের ব্যক্তিত্ব বেশ ভালভাবেই তাদের শ্রেণি সম্পর্কের হাতে নির্ধারিত হয়। তাদের মাঝের পারস্পরিক সম্পর্ক যদিও দুই ব্যক্তির মাঝের সম্পর্ক, কিন্তু সর্বোপরি তা “সামাজিক চরিত্র মুখোশের” সম্পর্ক। এই সম্পর্ক নির্দিষ্ট ব্যক্তির নয়, তা বরং প্রমিত “গড় ব্যক্তি”র। মার্কস বিশ্বাস করতেন, আশা করতেন যে “বিপ্লবী সর্বহারা জনসমাজে” ব্যাপারটা উল্টে যাবে। ব্যক্তি বা স্বতন্ত্র সেখানে স্বতন্ত্র হিসেবেই অংশগ্রহণ করবে। মার্কসের মতে, মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্ধারণকারী শর্তগুলো আগে “নিছক দৈবের হাতে ছেড়ে দেয়া হতো। ফলে তারা আলাদা ব্যক্তির ওপরে একটা স্বাধীন অস্তিত্ব হয়ে চেপে বসত। ব্যক্তি হিসেবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই এর কারণ। ” কিন্তু কমিউনিজম এবং সাধারণ নিয়ন্ত্রণে এই ব্যাপারটা “সামাজিক চরিত্র মুখোশের”, শ্রেণি এবং বর্ণের ব্যবস্থা হয়ে কাজ করবে না, তার ভিত্তি হবে স্বতন্ত্র মানুষের স্বাধীন জোট বা সংঘ।
ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে একটা মিথস্ক্রিয়া আছে: যেমন করে সমাজ নিজে মানুষকে মানুষ হিসেবে উৎপাদন করে, তেমনি সমাজও মানুষ দ্বারা উৎপাদিত হয়। ক্রিয়া এবং উপভোগ উভয়েই তাদের আধেয় এবং অস্তিত্বের ধরনে সামাজিক: সামাজিক ক্রিয়া এবং সামাজিক উপভোগ। প্রকৃতির মানবপ্রেক্ষিত কেবল সামাজিক মানুষের জন্য অস্তিত্ববান; কারণ কেবল তখনই প্রকৃতি তার জন্য মানুষের সঙ্গে বন্ধন হিসেবে-তার অস্তিত্ব অন্যের জন্য এবং অন্যদের অস্তিত্ব তার জন্য বহাল থাকে আর মানব বাস্তবতার জীবন উপাদান হিসেবে কেবল তখনই তার নিজের মানব অস্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে প্রকৃতি অস্তিত্বশীল থাকে। কিন্তু আবার যখন আমি বিজ্ঞানসম্মত, অন্যান্যভাবে ক্রিয়াশীল (অর্থাৎ এমন একটা ক্রিয়াশীলতায়, যেখানে আমিই কদাচিৎ অপরের সঙ্গে সরাসরি যোগ স্থাপন করি) তখনো আমার ক্রিয়াশীলতা সামাজিক; কারণ আমি এটা করি একজন মানুষ হিসেবে। শুধুমাত্র আমার ক্রিয়ার বিষয়বস্তুই যে আমার কাছে সামাজিক উৎপন্ন হিসেবে প্রদত্ত হয় তাই নয় (এমনকি চিন্তাকারী ব্যক্তি যাতে সক্রিয় সেই ভাষাও সমাজ উৎপন্ন) আমার নিজের অস্তিত্বও সামাজিক ক্রিয়া। আর তাই এই অস্তিত্ব আমি নিজেই তৈরি করেছি, করেছি সমাজের জন্য, সামাজিক সত্তা হিসেবে আমার নিজের চৈতন্য দিয়ে। এটা কোন সাদামাটা হিতবাদ নয়। কারোর কাজ সরাসরি সমাজের কাজে লাগার ব্যাপারও এটা নয়। এখানে ব্যাপারটা হলো ব্যক্তির সামাজিক স্বভাবের-সমাজের ফলাফল ও ন্যায্যতা প্রতিপাদন হিসেবে ব্যক্তিত্বের।
মানুষ তাই যতটা নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র (আর সংক্ষেপে তার বৈশিষ্ট্যই) তাকে একজন স্বতন্ত্র, এক বাস্তব স্বতন্ত্র সামাজিক সত্তা বানায়), ঠিক ততটাই খোদ নিজের জন্য কল্পিত এবং অভিজ্ঞাত সমাজের সমগ্রতা-আদর্শ সমগ্রতা-বিষয়ীগত অস্তিত্ব। ঠিক যেভাবে যে সমাজ অস্তিত্বের সম্পূর্ণ মানুষের সজাগতা ও বাস্তবতা উপভোগ এবং জীবনের মানব প্রকাশ উভয়ভাবেই বাস্তব জগতেও অস্তিত্ববান।
মার্কস ঘোষিত এই মানুষের সমগ্রতা, যাকে শিলার বলছেন “মানুষের স্বভাবের ভেতর মানবতা”, প্রথমে কেবল এক ভাব হিসেবে থাকে, অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে তা এখনো অবাস্তবায়িত এক সম্ভাবনা মাত্র। টুকরো, অসম্পূর্ণ, বিকৃত মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ মানুষে রূপান্তরিত করতে অক্ষম। সে এই রূপান্তর ঘটাতে পারে কেবল সমাজের বিকাশের মধ্য দিয়ে। নিজের সংবেদন, মরম, বুদ্ধিমত্তার মধ্য দিয়ে মানুষ যত বাইরের জগৎ অধিকার করে-আর এই অধিকার, এই নিজের করে নেয়া যত বেশি সংহত আর বহুপাক্ষিক হয়, তার সম্পূর্ণ মানুষ হওয়ার সুযোগ তত বেশি হয়।
মানুষ তার সমগ্র সারসত্তাকে সামগ্রিকভাবেই আত্মসাৎ করে-তার মানে বলতে গেলে এক সমগ্র মানুষ হিসেবে জগতের সঙ্গে তার প্রতিটি মানবিক সম্পর্ক-দেখা, শোনা, গন্ধ, স্বাদ, অনুভব, চিন্তা, পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা, চাওয়া, কাজ করা, ভালবাসা, সংক্ষেপে তার স্বতন্ত্র সত্তার সকল অঙ্গসমূহ আঙ্গিকে সরাসরি সামাজিক অঙ্গগুলোর মতই তাদের বিষয়গত বিকাশ অভিমুখকরণ অথবা তাদের বিষয়ের প্রতি বিকাশ অভিমুখকরণ এ বিষয়ের আত্মসাৎকরণ; মানব বাস্তবতার আত্মসাৎকরণ। বিষয়ের প্রতি তাদের বিকাশ অভিমুখকরণ, মানব বাস্তবতার প্রকাশ। এটা মানব ক্রিয়া এবং মানব যাতনা, কারণ মানবিক বিবেচনায় যাতনা মানুষের এক ধরনের আত্ম উপভোগ।
নিজের সংবেদন, বুদ্ধিমত্তা আর কল্পনার মধ্য দিয়ে মানুষ যে বিষয়কে নিজের করে, তা মানুষের নিজের বিষয়করণ হয়ে যায়। মানে সেই বিষয়কে আত্মভূত করে সে তার সাথে এক হয়ে যায়, সেগুলোকে নিজের সৃষ্টি বানিয়ে নেয় আর নিজের সত্তার অংশ করে নেয়। সংবেদনগুলোকে মনুষ্যোচিত করতে এবং তাদের মানব সংবেদন হওয়ার শিক্ষা দেয়ার জন্য মানব জাতির সম্পূর্ণ বিকাশ দরকার। মার্কস যখন এইসব অন্তর্ভুক্ত নিজের করে নেয়ার কথা আর “সমস্ত সংবেদনের অর্পিত গুণে সজ্জিত” মানুষের কথা বলেন, তখন তিনি আসলে যতটা সম্ভব বিস্তৃত এক সৃজনশীল, শৈল্পিক কাজের কথা বোঝান। এ কারণে মার্কসের কাছে ভালবাসা হচ্ছে সেই রকম নিজের করে নেয়ার এক প্রামাণিক রূপ। দখলদারি আর বাণিজ্য ও মুনাফার আজকের জগতে এই মানবিক কাজ “আমার এটা আছে, ওইটা আছে” নিতান্ত এই বোধে পর্যবাসিত হয়েছে। মার্কস এই “আছে” মানসিকতার বিরুদ্ধে খুব আবেগী ভাষায় কথা বলেন। এই “আছে” মানসিকতা তাৎক্ষণিক বস্তুগত দখলদারিকেই “জীবন ও অস্তিত্বের অনন্য উদ্দেশ্য ১৫ বলে মনে করে। এই মানসিকতা খোদ ভালবাসাকেও সংক্রমিত করেছে। এর হাতে পড়ে মানব আর মানবীর সম্পর্ক মালিকানা আর আধিপত্যের সম্পর্কে বদলে গেছে। হালের বিবাহের ধরন: “এক ধরনের একচেটিয়া ব্যক্তি সম্পত্তি”-আর নারীদের ওপর সাধারণ মালিকানার যে দাবি “স্থূল ও অচিন্তাশীল কমিউনিজম” তোলে, দুটোই ধারণার মধ্য দিয়ে নিজের করে নেয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত।আর তাই এর মানে মানুষকে জিনিসের স্তরে নামিয়ে আনা।

ছবি: নেট থেকে সংগৃহিত।
নারীর ক্ষেত্রে তাদের যে প্রস্তাবনা তাতে নারীরা জনসম্প্রদায়গত লালসার হাতের পুতুল মাত্র। তা প্রকাশিত হয় এক অসীম অবমাননায়, যেখানে পুরুষ তার নিজের জন্য অস্তিত্বশীল। এই প্রস্তাবনায় একটা খোলামেলা, প্রতারণাশীল, সোজাসাপ্টা এবং অনাবৃত প্রকাশ আছে। এবং সেই প্রকাশ নারী ও পুরুষের সম্পর্কের-যাতে স্বাভাবিক এবং সরাসরি প্রজাতি সম্পর্ক ধারণা করে নেয়া হয়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সরাসরি, স্বাভাবিক এবং প্রামাণিক সম্পর্কই নারী ও পুরুষের সম্পর্ক। এই স্বাভাবিক প্রজাতি সম্পর্কে পুরুষের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কই প্রত্যক্ষভাবে মানুষের সাথে তার সম্পর্ক, ঠিক যেমন মানুষের সাথে তার সম্পর্ক প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতির সাথে তার সম্পর্ক-তার নিজস্ব স্বাভাবিক গন্তব্য। তাই এই সম্পর্কে সংবেদনগতভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য সংকুচিত সত্যতায় সেই বিস্তৃতি সীমা প্রকাশিত হয়, যাতে মানব সারসত্তা পুরুষের কাছে প্রকৃতি হয়ে গেছে অথবা যাতে প্রকৃতি তার কাছে হয়ে গেছে পুরুষের মানব সারসত্তা। এই সম্পর্ক থেকেই তাই কেউ চাইলে মানুষের বিকাশের সামগ্রিক স্তর বিচার করতে পারে। এই সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হতে আরো বোঝা যায় যে প্রজাতি সত্তা হিসেবে, পুরুষ হিসেবে, মানুষ কতটা নিজে যা-তা হয়ে উঠল আর কতটাই বা নিজেকে অনুধাবন করল। পুরুষের সাথে নারীর সম্পর্ক হলো মানব সত্তার সাথে মানব সত্তার সবচাইতে স্বাভাবিক সম্পর্ক। তাই এটি সেই বিস্তৃতি উন্মোচন করে, যাতে পুরুষের স্বাভাবিক আচরণ হয়ে গেছে স্বাভাবিক সারসত্তা। এই বিস্তৃতিতে তার মানব স্বভাব তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। এই সম্পর্ক আরো একটি বিস্তৃতি প্রকাশ করে। তা হলো পুরুষের প্রয়োজনটি কতদূর মানবিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে; আর তাই তা প্রকাশ করে অন্য ব্যক্তি তার জন্য ব্যক্তি হিসেবে কতটা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে-যে নিরিখে সে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে একই কালে একজন সামাজিক সত্তা।
এইভাবে সবচাইতে স্বাভাবিক যে সম্পর্ক তা হয়ে ওঠে মানবিকীকরণের মানদণ্ড। গ্যেটে একে বলতেন চেহারাহীন যৌনতা হতে “উচ্চতর যৌন সম্মিলনে” বিকশিত হওয়া, সংবেদন, মরম আর মনের সম্মিলন, অপরকে আমারই মত আরেক সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া। এই প্রক্রিয়া প্রকৃতিকে ধ্বংস না করে তাকে বাড়তে দেয় যতক্ষণ না সে সত্যিকারের মানব স্বভাব হয়ে ওঠে। ১৮৪৩ সালে মার্কস এক সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করলেন, নাম জেনি ফন ভেস্টাফলেন। ১৮৫৬ সালের ২১ জুন তিনি লন্ডন হতে এক চিঠিতে জেনিকে লিখছেন:
ক্ষণিকের বিরহ মন্দ নয়। যা কিছু বর্তমান, তার সবকিছু এক রকম লাগে, আলাদা করা যায় না। দু’টো উঁচু মিনার কাছাকাছি থাকলে বামন বলে মনে হয়। অথচ প্রতিদিনের ছোট ব্যাপারগুলোও কাছে আসলে কত বড় হয়ে যায়। কাছে থাকা আবেগের চেহারা নেয়া ছোট অভ্যাসগুলো চোখের আড়ালে গেলেই হারিয়ে যায়। দূরে গেলে বড় আবেগগুলো হয়ে যায় ছোট অভ্যাস। তারাই আবার দূরত্বের জাদুর ছোঁয়ায় বড় হয়ে সামনে আসে। আমার প্রেমও তেমন। তুমি যদি স্বপ্নেও আমার কাছ হতে দূরে যাও, সেই দূরত্ব আমার প্রেমে সেই ছাপ ফেলে, যে ছাপ বৃক্ষের ওপর ফেলে রোদ আর বৃষ্টি। আমার প্রেম বৃক্ষের মতই বেড়ে ওঠে। তুমি যখনই দূরে যাও, আমি তোমার জন্য আমার ভালবাসাকে আসল রূপে দেখতে পাই। সেই প্রেম মহিরূহ, তার ডালে, পুষ্প-পল্লবে আমার মনের, হৃদয়ের সব শক্তি ঝলমল করে ওঠে। কী এক তীব্র আবেগে আমি নিজেকে আবার মানুষ বলে অনুভব করি। আধুনিক শিক্ষা নিখুতভাবে তৈরি হয়েছে আমাদের সবাইকে ছোট, দুর্বল, দ্বিধাচ্ছন্ন করে তোলার উদ্দেশ্যে। সেই শিক্ষায় জড়িয়ে আমরা সবকিছুকে সন্দেহ করি। কিন্তু প্রেম, ফয়েরবাখের মানুষ প্রেম অথবা মলেসখটের বিপাকবাদ নয়, সর্বহারার প্রেমও নয়, বরং প্রেমাস্পদের জন্য প্রেম, আরো ঠিক করে বললে তোমার প্রেম, মানুষকে আবার মানুষ করে তোলে।… ব্রাহ্মণ আর পিথাগোরাস তাদের পুনর্জন্ম, খ্রিস্টানরা তাদের পুনরুত্থানের তত্ত্ব মাথায় তুলে রাখুন, আমি তার পরোয়া করি না। “তার আলিঙ্গনে ডুবে, তার চুম্বনে আবার বেঁচে উঠি”, হ্যাঁ, তোমার আলিঙ্গনে, তোমারই চুম্বনে আমি আবার বেঁচে উঠি। এভাবে, ভালবাসার মাঝ দিয়ে নিজের করে নেয়ার মাধ্যমে প্রকৃতি হয়ে ওঠে মানব প্রকৃতি।
নিজের স্বভাবকে মানবায়িত করে, অপর মানুষকে জিনিসের স্তরে নামাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে, তার বদলে প্রকৃতির বিষয়কে নিজের করে, একে মানবিকভাবে অনুধাবনযোগ্য করে, স্বীকৃতি দিয়ে, তাকে মানবিকভাবে নিজের করে মানুষ নিজের সত্তার সক্ষমতা আর প্রাচুর্যের বিকাশ ঘটাতে পারে। আছে ধারণার মধ্য দিয়ে নিজের করা, খণ্ডিত করার মধ্য দিয়ে সম্ভাবনাময় প্রাচুর্যকে ব্যক্তি সম্পত্তির জোড়াতালি বানিয়ে ফেলার এই কারবার মানুষকে “নির্বোধ আর একপেশে” বানিয়ে ফেলে। কিন্তু অধিকারের মধ্য দিয়ে নিজের করে নেয়া পূর্ণ উৎপাদনশীল সমাজের দিকে যাওয়ার অনিবার্য পদক্ষেপ ছিল এবং আছে। এভাবেই সক্ষমতার সঙ্গে সমাজে চাহিদা ধাপে ধাপে বাড়ে আর মানুষ জিনিসের স্তরে নেমে আসে না, অন্যভাবে বললে, সত্যকারের মানবিক সমাজ গড়ে ওঠে।
মার্কস কোন ছিচকাদুনে নীতিকথার প্রচারক ছিলেন না। দখল করার মধ্য দিয়ে নিজের করে নেয়া, ব্যক্তি সম্পত্তির শাসন আর পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের বিমানবিকীকরণের দানবিক স্বভাব উন্মোচন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একে ঐতিহাসিক বিকাশের আবশ্যিক স্তর হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। তিনি দেখেছেন যে, এর মধ্যেই পরিপক্ক হয়ে উঠছে এক নতুন বাস্তবতা।
ব্যক্তি সম্পত্তি আমাদের এতটাই বেকুব এবং একপেশে করেছে যে, আমরা যখন একটা বিষয় প্রাপ্ত হই তখন তা কেবলই আমাদের-অথবা তা আমাদের জন্য পুঁজি হিসেবে অস্তিত্বশীল। অথবা তখন এটা সরাসরি ভোগদখলকৃত, খেয়ে নেয়া, পান করে নেয়া, পরিধানকৃত, বাসকৃত-সংক্ষেপে তা আমাদের দ্বারা ব্যবহৃত। সকল শারীরিক এবং মানবিক ইন্দ্রিয়গুলোর স্থানে তাই চলে এসেছে এই সকল ইন্দ্রিয়ের পুরোদস্তুর বিচ্ছিন্নতা, অধিকারবোধের সংবেদন। মানবসত্তা যাতে তার অন্তর্গত সম্পদ বাইরের জগতে তুলে আনতে পারে তার জন্য তাকে চরম দারিদ্র্যে পর্যবসিত করা হয়।
স্থূল ব্যবহারিক প্রয়োজনের হাতে আবদ্ধ সংবেদন দুঃখজনক রকম সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। একজন ভুখা মানুষের কাছে, খাদ্য মানুষের খাবার মত করে দেয়া হলো কি না-তার বিশেষ মূল্য নেই। সে কেবল এর খাবার হিসেবে বিমূর্ত অস্তিত্ব নিয়েই মাথা ঘামায়। এ যেন টিকে থাকতে পারে সবচাইতে স্কুল রূপে, আর জানোয়ারদের খাদ্য জোগাড়ের সঙ্গে এর তফাৎ কী তা বলা অসম্ভব।
এর অর্থ কী? এর অর্থ হলো এই যে, আর কোন মানুষ ভুখা থাকা চলবে না। এর মানে, সমাজকে শুধু সবচেয়ে আদিম প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হলেই হবে না, তাকে এগিয়ে যেতে হবে আরো উচ্চতর, আরো পৃথক পৃথক প্রয়োজন মেটানোর দিকে, যে প্রয়োজন আর জান্তব নয়, বরং মানবিক। সেই ভবিষ্যতের মাল-সামান ব্যক্তি সম্পত্তির সমাজেই জমা হয়।
ব্যক্তি সম্পত্তির সঞ্চলন, এর সম্পদ আর পাশাপাশি এর দুর্দশা-এর বস্তুগত ও মরমি সম্পদ ও দুর্দশার মধ্য দিয়ে মুকুলিত সমাজ এই বিকাশের জন্য সব মালমসলা হাতে পেয়ে যায়। ঠিক এমনিভাবেই প্রতিষ্ঠিত সমাজ মানুষকে তার সত্তার সমস্ত সমৃদ্ধি দিয়ে উৎপন্ন করে-ধনী মানুষকে উৎপন্ন করে সমগ্র সংবেদন দিয়ে যত্ন করে সাজিয়ে গুছিয়ে-সমাজের বিদ্যমান বাস্তবতার হিসেবে।
এর সমস্ত স্ববিরোধসহ বুর্জোয়া সমাজকে মার্কস এমন এক সমাজ হিসেবে দেখেছেন, যা হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মাঝে আছে। কমিউনিজম এমন এক সমাজ, যা এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। মার্কস কমিউনিজমকে ব্যক্তি সম্পত্তির সরল অস্বীকৃতি হিসেবে আশা করেননি। এটা বরং প্রাচুর্যের, মানবতার আর সমন্বিত বুদ্ধিমত্তার এক জগতে ব্যক্তি সম্পত্তির ইতিবাচক বিলোপ:
মানুষের মাধ্যমে এবং মানুষের জন্য মানব প্রকৃতিকে বাস্তবে নিজের করে নেয়া।
মার্কস যেভাবে কমিউনিজম অনুমান করেছেন সে মতে তা “মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির আর মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈরিতার নির্ধারক সমাধান”। তিনি আশা করেছেন যে, কমিউনিজমের মানে হবে “প্রকৃতিবাদ” (মানে প্রকৃতির জোগান দেয়া সিদ্ধান্তসূত্র) হতে “মানববাদে” (মানে সমগ্র, সচেতন আর বিভক্ত না থাকা মানুষের পূর্ণ প্রস্ফুটন) রূপান্তর। সেই তরুণ কাল হতে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত মার্কসের উদ্দেশ্য ছিল সংবেদনকে দুর্বল নয়, বরং মানবায়িত করা; মন দিয়ে শরীর বা শরীর দিয়ে মনকে প্রতিস্থাপন নয়; বরং উৎপাদন বা উপভোগের জন্য সকল ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো; বস্তুগত বা মরমি নিঃস্বতা নয়, বরং এই জগৎ ও এর সমস্ত সম্ভাবনাকে সর্বব্যাপীভাবে নিজের করে নেয়া; কোন আদর্শ ছকে বেঁধে দেয়া আর অব্যক্তিকরণ নয়, বরং অপরের সঙ্গে মুক্ত জনসমাজে বাস করা স্বতন্ত্রতার বহুমুখী স্বভাব।
মার্কস কি তাহলে কমিউনিজমকে কোন চূড়ান্ত স্তর, কোন দিব্যধাম হিসেবে দেখেছেন? না, তাতো নয়ই, বরং উল্টো। তাঁর কাছে কমিউনিজমের মানে সত্যিকারের মানব বিকাশের সূচনা মাত্র। স্বপ্ন সব সময়ই বাস্তবের আগে আসে। কর্মের আগে আসে চিন্তা।
ব্যক্তি সম্পত্তির ভাব বিলোপ করতে কমিউনিজমের ভাবটি একদম যথেষ্ট। বাস্তব ব্যক্তি সম্পত্তিকে বিলোপ করতে বাস্তব কমিউনিস্ট ক্রিয়া লাগে। ইতিহাস এদিকেই নিয়ে যাবে; আর এই সঞ্চলন, যাকে আমরা এর মধ্যেই তত্ত্বে আত্ম-অতিক্রমকারী সঞ্চলন বলে জেনেছি, বাস্তবে তা খুব কর্কশ এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া গঠন করবে। তবে যাত্রাতেই এই ঐতিহাসিক সঞ্চলনের শুধু লক্ষ্যই নয়, সীমিত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ৩০ মার্কস আসলে যা বলেছেন
সচেতনতা এবং একে ছাপিয়ে যাওয়া এক চৈতন্য অর্জন করাটাকে আমরা অবশ্যই একটা সত্যিকারের অগ্রগতি বলে বিবেচনা করব।
চৈতন্য তখন লক্ষ্যের চাইতে আর ঐতিহাসিক প্রগতির অনুকরণের চাইতে দূরে এগিয়ে যায়; এটা কমিউনিজমকে কোন চূড়ান্ত স্তর নয়, বরং এমন এক বিকাশের পর্ব মাত্র হিসেবে দেখে, যে বিকাশের নীতিগতভাবে কোন শেষ নেই। কিন্তু তার স্বপ্নের দেশে বিশ্বাস করার মত সাহস আছে।
পরবর্তীকালে মার্কস দূরবর্তী স্বপ্নের দেশের এই উজ্জ্বল স্বপ্ন অপেক্ষাকৃত কম রঙিনভাবে উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু তিনি কখনো তা পরিত্যাগ করেননি। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তি মালিকানার ইতিবাচক বিলোপ, শ্রমের বিজ্ঞানভিত্তিক স্বভাব, মানুষের জায়গায় যন্ত্র কাজে লাগানো সমগ্র মানুষের অস্তিত্ব বাস্তব করবে। আর এর ফলে মানুষ তার সম্ভাবনাময় সামর্থ্যের পূর্ণ পরিসর মেলে ধরতে সক্ষম হবে।
মার্কস (এঙ্গেলস আরো বেশি) প্রথমে বিশ্বাস করতেন যে সমগ্র মানুষ গড়ে উঠবে সামাজিকভাবে আবশ্যিক, প্রয়োজনীয় উৎপাদনের পরিমণ্ডলের ভেতরে যন্ত্রকে আয়ত্তে নিয়ে এবং নিজের কার্যকলাপের স্বভাবে নিরন্তর পরিবর্তন এনে। তবে মার্কস পরে এই ধারণা পরিত্যাগ করেন। ১৮৫৭-১৮৫৮ সালের দিকেই “গ্রন্ড্রিজে”র (রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের পর্যালোচনার ভিত্তি) খসড়াতে তিনি জোর দিচ্ছেন “সবার জন্য সময় বন্ধনহীন হয়ে যাওয়ার ফলাফল হিসেবে ব্যক্তির জন্য শিল্পসুলভ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা”র ওপর। তবে তিনি এও সম্ভব ভেবেছেন যে, “উৎপাদনের প্রত্যক্ষ বস্তুগত প্রক্রিয়া” এর রূপ পরিত্যাগ করতে পারে “আবশ্যিকতা” হিসেবে।
তার শেষ কাজ, ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডে তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিমার্জন করেন।
সুতরাং সমাজের সত্যিকারের ধন এবং তার নিরন্তর সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নির্ভর করে না উদ্বৃত্ত-শ্রমের স্থায়িত্বকালের উপরে, নির্ভর করে তার উৎপাদনশীলতার উপরে, এবং কম-বেশি প্রাচুর্যপূর্ণ অবস্থাবলীর উপরে, যার মধ্যে তা সম্পাদিত হয়। বস্তুতপক্ষে, স্বাধীনতার এলাকা সত্যি সত্যি শুরু হয় কেবল সেখানেই, যেখানে শ্রম, যা নির্ধারিত হয় প্রয়োজন ও সাংসারিক চিন্তা ভাবনার দ্বারা তার বিরতি ঘটে; তাই স্বাধীনতার স্বাভাবিক অবস্থানই হচ্ছে সত্যিকারের বস্তুগত উপাদানের পরিধি ছাড়িয়ে। ঠিক যেমন অসভ্য মানুষকে তার অভাব মেটাবার জন্য জীবন পোষণ ও পুনরুৎপাদনের জন্য কুস্তি লড়তে হয় প্রকৃতির সঙ্গে, ঠিক তেমনি করতে হয় সভ্য মানুষকেও এবং তাকে তা করতে হয় সমস্ত সম্পূর্ণ মানুষের স্বপ্ন ৩১
সমাজ-ব্যবস্থায় এবং সম্ভাব্য সবরকমের উৎপাদন পদ্ধতিতে। তার বিকাশের সঙ্গে দৈহিক প্রয়োজনের এই পরিধি তার বিবিধ অভাবের ফলে বিস্তার লাভ করে; কিন্তু একই সঙ্গে বৃদ্ধি লাভ করে উৎপাদনের শক্তিসমূহ যারা পূরণ করে এই সমস্ত অভাব। এক্ষেত্রে স্বাধীনতা রূপ ধারণ করতে পারে কেবল সমাজকৃত মানুষের দ্বারা, সংঘবদ্ধ উৎপাদনকারীদের দ্বারা, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের লেনা-দেনাকে যুক্তিসিদ্ধ ভাব পরিচালন এবং প্রকৃতি কর্তৃক, তথা তার অন্ধ শক্তিসমূহ কর্তৃক শাসিত না হয়, তাকে তাদের সামূহিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা এবং ন্যূনতম কর্মশক্তি-ব্যয়ে এবং তাদের মানব-প্রকৃতির পক্ষে সর্বাধিক অনুকূল ও উপযুক্ত অবস্থাধীনে এই লক্ষ্য সাধন করার মাধ্যমে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তা তখনো থেকে যায় প্রয়োজন-পূরণের পরিধির মধ্যে। এই পরিধি ছাড়িয়েই শুরু হয় মানবিক শক্তির সেই বিকাশ যা নিজেই নিজের উদ্দেশ্য, স্বাধীনতার সত্যিকারের জগৎ কিন্তু যা কুসুমিত হতে পারে কেবল প্রয়োজন-পূরণের জগতের ভিত্তির উপরেই। কাজের দিনের দীর্ঘতা হ্রাস হচ্ছে তার মৌল পূর্বশর্ত।
বস্তুগত উৎপাদনের সংকীর্ণ বলয় পার হয়ে মানুষের সত্যিকারের জগৎ হিসেবে “স্বাধীনতার জগৎ”, বিজ্ঞান ও শিল্পের, প্রেম ও প্রশান্তির, জনসমাজ ও ব্যক্তিগত মুক্তির মধ্যে মানুষের ফুলের মত ফুটে ওঠা-এই অসাধারণ স্বপ্নের ছবির আদল আঁকা আছে তরুণ মার্কসের লেখায়। আর তা পরিণত ও বৃদ্ধ মার্কসের রচনাতেও অক্ষুণ্ণ ছিল। মার্কসের কাছে ইতিবাচক মানববাদের সারাংশ “বিমূর্ত”, সেই একঘেয়ে শ্রম নয়, যা মানুষকে তার নিজ সত্তার টুকরো অংশে পর্যবসিত করে। তা বরং সৃজনশীল কাজ, মানব সম্ভাবনার বিকাশ। এই বিকাশ নিজেই নিজের লক্ষ্য।

লেখক, অনুবাদক, সাংবাদিক।


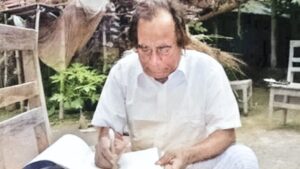

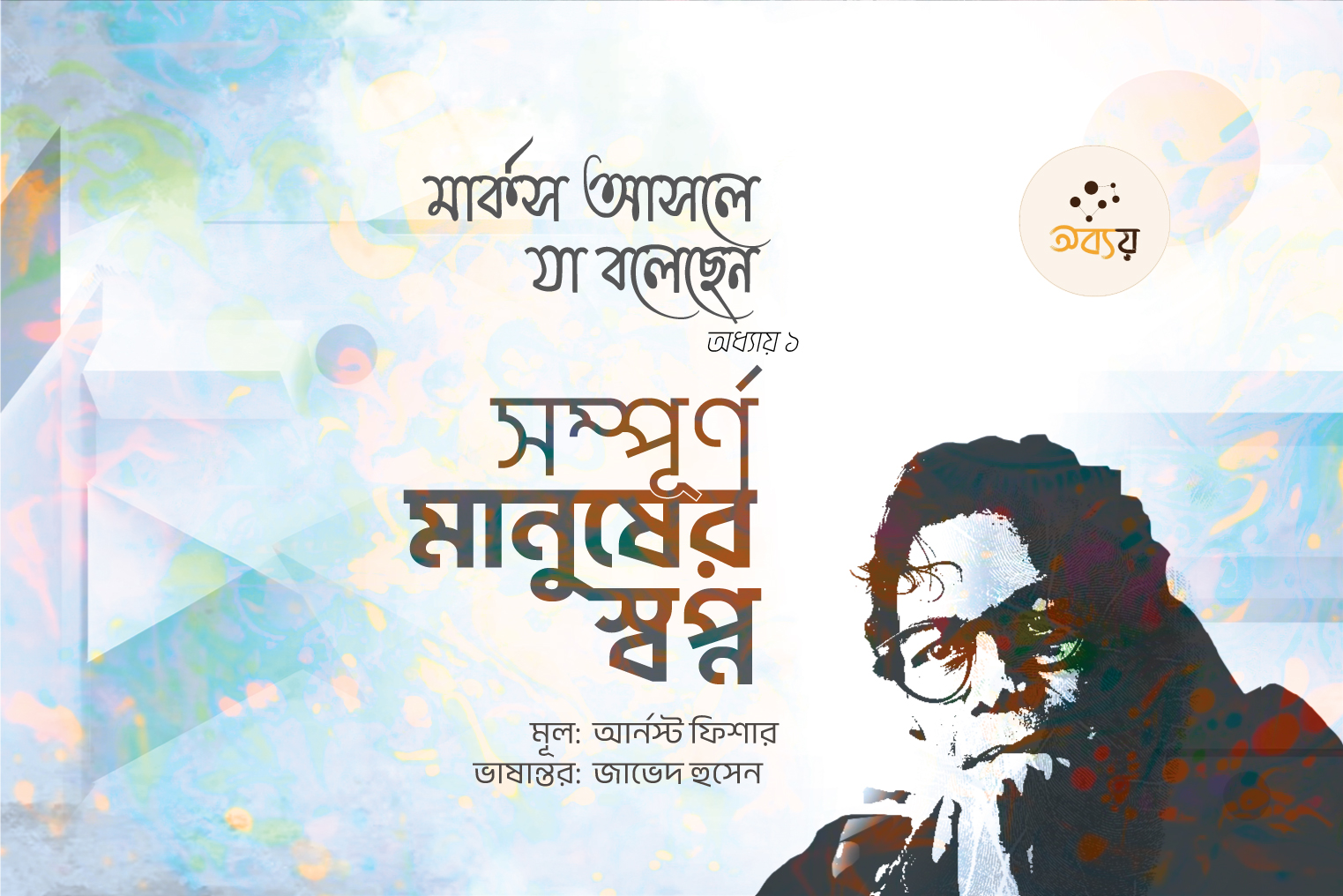
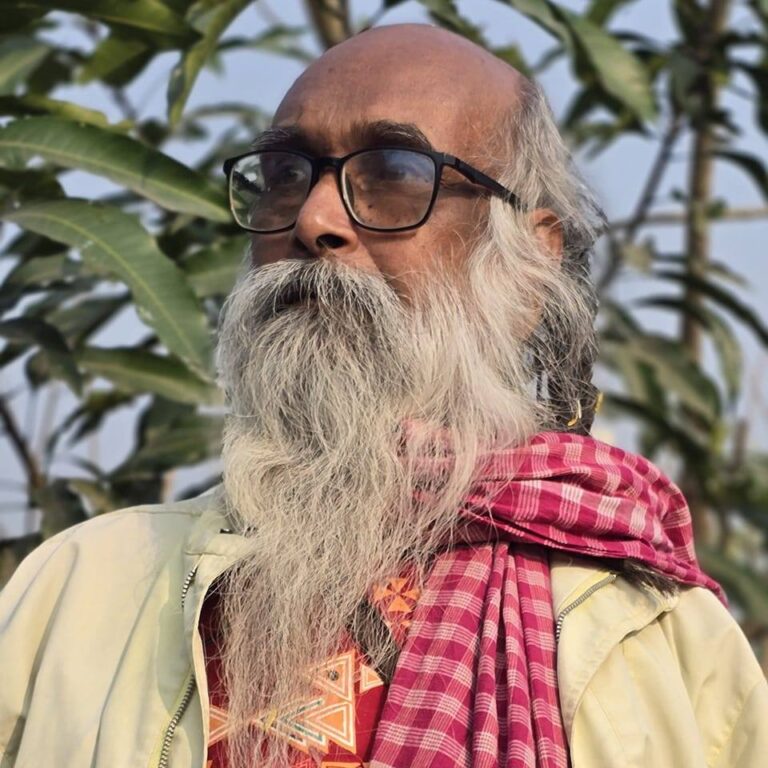
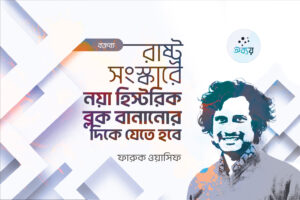
Leave a Reply